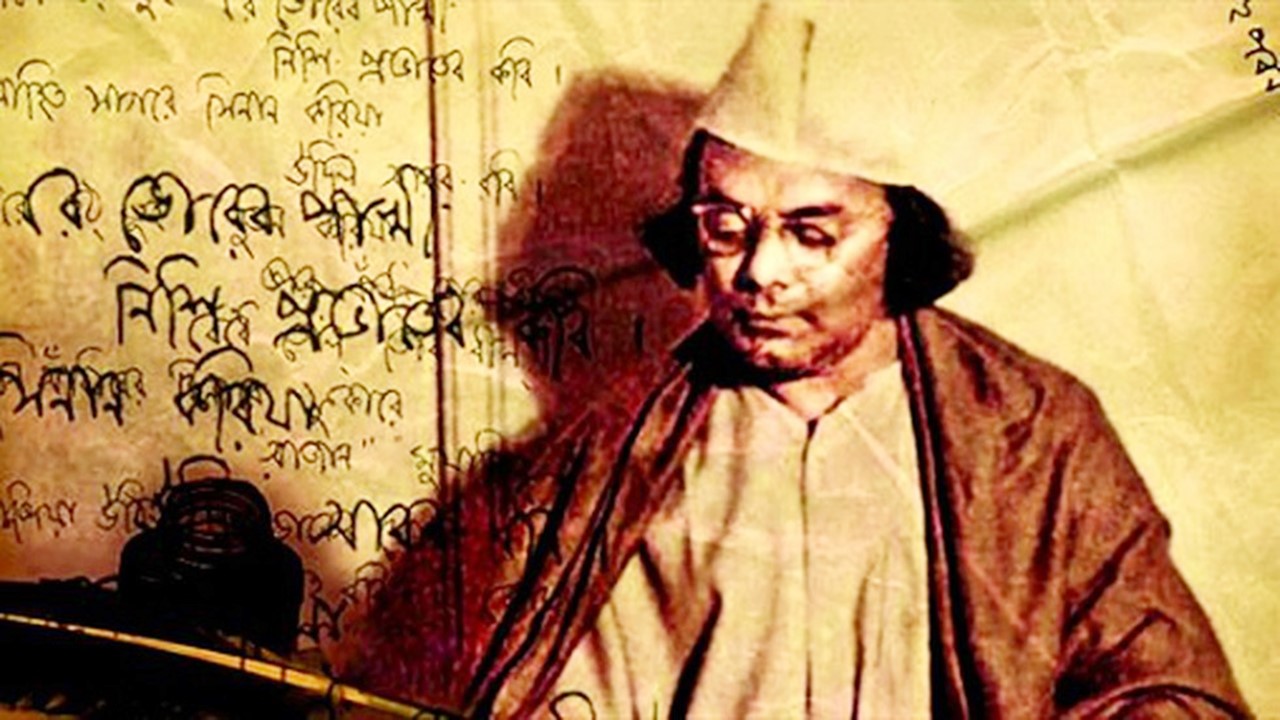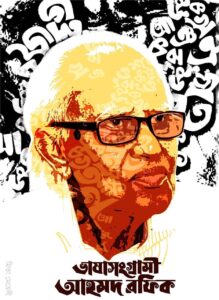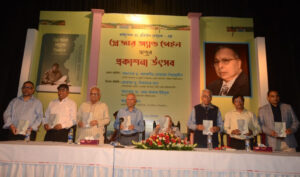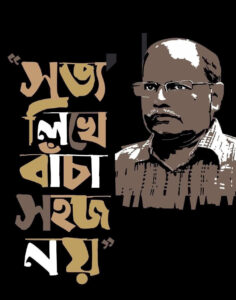ইসরাইল খান
সওগাত-যুগে মুসলিম সম্পাদিত ও প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকাগুলোর মধ্যে ‘ছায়াবীথি’ বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছিল। কিন্তু এই পত্রিকাটির পরিচয় ছিল অজ্ঞাত। এ-পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ একটি বিবরণ কেউ লেখেন নি। কারণ এর কোনো নথি সুলভ ছিল না। অথচ এটি কলকাতা থেকে ১৯৩৩ সনে একজন সপ্রতিভ তরুণ সম্পাদনা করেছিলেন। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁকে ‘মিতা’ বলে উল্লেখ করতেন। পরবর্তীকালে তিনি ‘বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস’(১৯৫০) লিখে ব্যাপক সমালোচিত হয়েছিলেন। নাম তাঁর অধ্যক্ষ নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান (১৯০৬-৮২)।
প্রখ্যাত সাহিত্যিক-শিল্পী শ্রীদিলীপকুমার রায় (১৮৯৭-১৯৮০) তাঁর গল্পগ্রন্থ ‘সোনালী স্বপন’ (১৯৩৩) পাঠ করে প্রশংসা করেছিলেন। সেই সুত্রে তিনি ‘গদ্য ও পদ্য’ নামে ছায়াবীথিতে দীর্ঘ একটি পত্রপ্রবন্ধও লিখেছিলেন। অবশ্য ছায়াবীথি সম্পাদনকালে তিনি ছিলেন শুধুই ‘নাজিরুল ইসলাম’।
নজরুলের সঙ্গে নাজিরুল ইসলামের নামের ব্যাবধান মাত্র একটি আ-কার। তখন তাঁর বয়স সাতাশ-আঠাশ। জসীমউদদীন, আবুল ফজল, আবু সয়ীদ আইয়ুব, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, লীলাময় রায় (অন্নদাশঙ্কর রায়), আবদুল কাদির, হুমায়ুন কবির, অজিতকুমার দত্ত, মহিউদ্দীন, বন্দে আলি মিয়া, সুফিয়া কামাল (তখন সুফিয়া এন হোসেন), মুহম্মদ এনামুল হক প্রমুখ সম্পাদকের সমকালীন সমবয়সীদের তারুণ্যদীপ্ত লেখায় যেমন তেমনি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী আবদুল ওদুদ, আবদুল হাকিম (বিক্রমপুরী), অমলেন্দু দাশগুপ্ত, প্রভাবতীদেবী সরস্বতী, শাহেদ সুহরাবর্দ্দি, শ্রীদিলীপকুমার রায়, আবদুর রশিদ, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, গোলাম মকসুদ হিলালী, কবিশেখর কালিদাস রায়, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্ প্রমুখের রচনায় সমৃদ্ধ ছিল ছায়াবীথি। বুলবুল যেমন রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ সেরা বাঙালি সাহিত্যিকদের যুক্ত করে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের প্রধান লেখকদের সমবেত করতে চেয়েছিলেন (এবং পেরেছিলেনও) তেমনি ছায়াবীথিরও প্রচেষ্টা ছিল পত্রিকাটিকে অসাম্প্রদায়িক চারিত্র্য দান করতে।
তাই মনীষী রামমোহন রায়ের প্রয়াণ শতবার্ষিক স্মরণানানুষ্ঠানে ধর্ম সম্মেলনের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিভাষণ এবং কলকাতা সিনেট হলে দেয়া রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাবিষয়ক বক্তৃতার সারাংশ এবং অন্যান্য রচনাংশ পুনর্মুদ্রণ করতেন। নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের বিস্তারিত প্রতিবেদন ছেপেছিলেন। শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু ও শিল্পী রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর আঁকা ড্রয়িংয়ের ব্লক ছেপে ছায়াবীথিকে বৈচিত্র্যপূর্ণ ও নান্দনিকতায় সমৃদ্ধ করার প্রয়াস গ্রহণ করেছিলেন। তবে ছায়াবীথি বুলবুলের মতো স্থায়িত্ব লাভ করে নি। হিসাব অনুযায়ীও এটি বিখ্যাত ‘বুলবুল’ এর ছয় মাসের অনুজ প্রসূণ ছিল।
বুলবুলের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১৩৪০-এ, ছায়াবীথি কার্তিকে। বুলবুলের সাথে যেমন কবি নজরুলের গভীর সম্পৃক্তার পরিচয় পাওয়া গেছে, তেমনি ছায়াবীথির সাথেও ছিল তাঁর আত্মিক সম্পর্ক। পত্রিকার নাম-কবিতা (‘ছায়াবীথি’) লেখেন কাজী নজরুল ইসলাম। প্রায় প্রতি সংখ্যায়ই তাঁর কবিতা না হলে গজল বা কীর্তন বা আধুনিক গান হতো ছায়াবীথির প্রথম রচনা।
‘মুসলিম বাংলা সাহিত্য’-গ্রন্থের লেখক ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক কবি নজরুলকে নিয়ে রচনা করেন দীর্ঘ গবেষণা-প্রবন্ধ ‘তারুণ্যের কবি নজরুল” (এই দামি ঐতিহাসিক লেখাটি এখনও অগ্রন্থিত রয়ে গেছে!)। ‘বিষের বাঁশী’ কাব্য অবলম্বন করে বিপ্লববাদী সাহিত্যিক-সাংবাদিক শ্রীঅমলেন্দু দাশগুপ্তও দীর্ঘ একটি প্রবন্ধ লেখেছিলেন ‘বিষের বাঁশীর সৈনিক কবি’ শিরোনামে। (নজরুল জীবনীর মূল্যবান উপকরণ এই রচনাটিও অদ্যাবধি অসংগৃহীত ও অসংকলিত।) এতো অল্প বয়সে কোনো কবিকে নিয়ে লিখিত প্রবন্ধ-সমালোচনা খুব অল্প-সংখ্যক কবিরই ভাগ্যে জুটেছে। তাঁকে নিয়ে তুলনামূলক প্রবন্ধ ও আলোচনা লেখা হচ্ছে। তাঁর প্রতিকী নাম নতুন নতুন হচ্ছে তো হচ্ছেই। এইসব রীতিমতো বিরল ঘটনা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে।
সৈনিক কবির সমকালীন তরুণতরদেরও লেখার তখন জোয়ারের বেলা। জসীমউদদীন, হুমায়ুন কবির, আবদুল কাদিরের সুলিখিত রচনা ও নাজিরুল ইসলাম ও অন্য লেখকদের ধারাবাহিক উপন্যাস, গল্প ; আর ‘কলস্রোতা’ নামের আলোচনা-সমালোচনা ও মতামতের সম্পাদকীয় বিভাগের তথ্যসমূহ আজ ইতিহাসের আকরে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এই পত্রিকার কপিগুলো ভয়াবহরূপে দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেছে। ১৯৯৩-৯৮ সময়ে কলকাতায় কাজ করবার সময়ে দ্বিতীয় বর্ষের মাত্র তিনটি সংখ্যার সন্ধান পেয়েছিলাম ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে। তারই ভিত্তিতে লিখেছিলাম একটি ছোট্ট আলোচনা ‘মুসলিম সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকা’ শীর্ষক সন্দর্ভে। কিন্তু প্রথম বর্ষের একটিও সংখ্যা না-দেখা থাকায় তা ছিল অত্যন্ত অপূর্ণাঙ্গ একটি রচনা। সম্প্রতি মনীষী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের সংগৃহীত পত্রিকার ভিড়ে এই দুর্মূল্য ছায়াবীথির প্রায় ৯০ ভাগ সংখ্যারই সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। তারই ফসল বর্তমান রচনা।
বিশ শতকের বিশের দশকে যে বাঙালি মুসলমানেরা সাহিত্য ক্ষেত্রে হীনমন্যতায় ভুগতেন না, তা ছায়াবীথির পৃষ্ঠাগুলোও প্রমাণ করছে। এই পত্রিকার পাতা উল্টে যাঁরা মুসলমানদের সাহিত্য প্রয়াসের ব্যাপারে গৌণ ধারণা পোষণ করতেন, তাঁরা অবশ্যই খুশি হবেন। কেউ সহজে বিশ্বাস করতে চাইবেন না যে, এটি পেছিয়ে থাকা মুসলমানদের কোনো সাহিত্য পত্রিকা। ছাপা, গেটআপ-মেকআপ, অলঙ্করণ, মুদ্রণ-পারিপাট্য, আর্টিস্টদের আঁকা ছবির ব্লকের ব্যবহার ও শিল্পসম্মত উপস্থাপন এবং সুচিন্তিত রাজনৈতিক-সামাজিক বিষয়ের সম্পাদকীয় (কলস্রোতা)-তে দৃঢ় বক্তব্য সন্নিবেশ সবমিলিয়ে এক কথায় ছায়াবীথি ছিল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চমৎকার একটি সাহিত্য পত্রিকা।
‘ছায়াবীথি’ নামে নজরুলের নাম-কবিতার চারটি লাইন—
‘‘স্নিগ্ধ শীতল তৃণাস্তীর্ণ এই ছায়া-বীথি তলে
রচেছি কুঞ্জ শ্রান্ত পথিক জুড়াবে খানিক ব’লে।
ঝরা পাতা আর ফুলদল দিয়া রচিয়াছি হেথা পথ,
এই পথ দিয়া যাবে সুন্দর, বন্ধুর মোর রথ।’’
দু’বছরের মতো চালু থাকা পত্রিকাটির প্রায় প্রতি সংখ্যার প্রথম লেখাটিই ছিল নজরুল ইসলামের। ছাপা শুরুর সময় সংগৃহীত না-হলেও শেষের দিকে হলেও পত্রিকাটির লক্ষ্য ছিল নজরুল-এর কোনো না কোনো লেখা তাঁরা রাখবেনই। নজরুলেরও ছিল এটা সঙ্গীত-সৃষ্টির জোয়ারের কাল। তিনি ছায়াবীথিতে বেশির ভাগই দিয়েছেন গান, অথবা গানের মতো কবিতা বা অনূদিত রুবাইয়াৎ। পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য, কোনো প্রারম্ভিকী বা সূচনা বক্তব্য না থাকায় কে নাম দিয়েছিলেন পত্রিকার বা কে বা কারা ছিলেন উৎসাহদাতা— কিছুই জানা যায় না। তবে, নজরুল-চর্চার প্রবণতা দেখে অনুধাবন করা যায়—এর সকল লেখক সমালোচক ও পত্রিকার কর্তৃপক্ষ নজরুল ইসলামকে বড় মাপের প্রতিভা হিসেবে অতিউচ্চ শ্রদ্ধার আসনে রেখেছিলেন।
ছায়াবীথিতে নজরুলের যেসকল গান/কবিতা ছাপা হয়েছিল তার প্রথম এক-দুই লাইন করে উল্লেখ করা হল—
প্রথম সংখ্যার ‘ছায়াবীথি’ কবিতার পরে দ্বিতীয় সংখ্যায় ছাপা হয়—রুবাইয়াৎ-ই ওমর খৈয়াম। তৃতীয় সংখ্যায় গান—ঘুমাও ঘুমাও দেখিতে এসেছি,/ভাঙিতে আসিনি ঘুম; চতুর্থ সংখ্যায়—গান—কলঙ্ক আর জ্যোৎস্নায় মেশা/তুমি সুন্দর চাঁদ; পঞ্চম সংখ্যায়—গান— ‘বুনো ফুলের করুণ সুবাস ঝুরে/নাম-না-জানা বনের পাখি!; ষষ্ঠ সংখ্যায়—ভজন— বহু পথে বৃথা ফিরিয়াছি প্রভু/আর হইব না পথহারা।; সপ্তম সংখ্যায়— গান—একি অপরূপ রূপে মা তোমায় হেরিনু পল্লী-জননী।/ ফুলে ও ফসলে কাদা মাটী জলে ঝলমল্ করে লাবণী।।’; অষ্টম সংখ্যায়—গান—‘রাত্রি শেষের যাত্রী আমি/যাই চলে যাই একা।; দশম সংখ্যায়—গান—‘আমি ময়নামতীর সাড়ী দেবো চল আমার বাড়ী/ও গো ভিন্-গেরামের নারী।; একাদশ সংখ্যায়—গান—আঁধার রাতের তিমির দুলে আমার মনে/দুলে গো আমার ঘুমে জাগরণে !“; দ্বাদশ সংখ্যায়—গান—শিউলি ফুলের মালা দোলে/শারদ-রাতের বুকে ঐ।” ; দ্বিতীয় বর্ষ ২য় সংখ্যায়—গান—গানের বুলবুলি (‘ঘুমিয়ে গেছে শ্রান্ত হয়ে আমার গানের বুলবুলি’); দ্বিতীয় বর্ষ ৩য় সংখ্যায়—গান—গত রজনীর কথা পড়ে মনে/রজনী গন্ধার মদির গন্ধে।; দ্বিতীয় বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা ফাল্গুন ১৩৪১— গান—তোমার হাতের সোনার রাখী/আমার হাতে পরালে।..’’ ; দ্বিতীয় বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যায়—গান/কীর্ত্তন—‘তব চরণ প্রান্তে মরণ বেলায়/শরণ দিও হে প্রিয়’; দ্বিতীয় বর্ষ ৮ম সংখ্যায়—গান—তব যাবার বেলা বলে যাও মনের কথা।/কেন কহিতে এসে চলে যাও চাপিয়া ব্যথা।।”
সম্পাদক নাজিরুল ইসলাম নিজের দুটি ধারাবাহিক উপন্যাস—জীবনের জয়যাত্রা ও দুর্ব্বিপাক ছাড়াও আর্ট ও সৌন্দর্য্যতত্ত্ব বিষয় ছাড়াও নানাবিষয়ে প্রবন্ধও রচনা করেন। আহমেদ মনির মিখেলভিচ্ গারসিনের রাসিয়ান গল্প থেকে অনুবাদ করেন সিগনালার। প্রধানতম লেখক ছিলেন জসীমউদদীন ও হুমায়ুন কবির।
জসীমউদদীন-এর কবিতা ‘ নতুন সমাজ’
‘‘সোণামনি ভাইটি আমার লক্ষ্মীমনি বোন,
তোদের কেন ভালবাসি সেই কথাটি শোন।
একটি ছোট চিঠির লাগি ব্যাকুল হয়ে রই,
দেশ বিদেশে পদ্য করে তোদের কথা কই ।
কারণ তোরা এই পৃথিবীর নতুন-চলা পথে,
দেবতা হয়ে এসেছিস যে শিশুকালের রথে,
মায়ের মুখের সোহাগভরা আদরভরা ডাকে,
শিখেছিস যে আদর করে ডাকতে যাকে তাকে।
পরও আপন চিনিসনে তাই সবায় ভালবাসে।
আপন করে নিতে পারিস মিষ্টি মুখে হেসে।
এই জগতের মোরাও মানুষ অনেক ছিল আশা।’’
হুমায়ুন কবিরের ‘সমাপ্তি’-র কয়েকটি চরণ—
‘একদিন সাঙ্গ হবে ধরণীতে জীবনের ধারা
আজি হতে লক্ষ বর্ষ পরে,
সমুদ্র পর্ব্বতময়ী এ রম্য ভুবন হবে হারা
অন্তহীন ধ্বংশের গহ্বরে।
কিশোর কিশোরী হিয়া প্রণয়ের প্রথম স্পন্দনে
কাঁপিবে না আনন্দ শঙ্কায়।
ধ্বনিবে দিবসরাত্রি মহাশূন্য প্রলয় গর্জ্জনে
ভীতিহীন ঘন তমসায়।’’
ইমাউল হক (কবিতা) লিখেছিলেন—‘ভালবাসা’— “ভাল যে বাসনা তাই বলনা খুলিয়া,/মিছামিছি কেন তুমি কর তার ভান;/প্রেমের আলোকে সখি, রাঙা যার হিয়া/ তার কি থাকিতে পারে ভাল-মন্দ জ্ঞান? # ব্রাকুল সমুদ্র যবে চাঁদেরে হেরিয়া/পরশ পাইতে তার হয় আগুয়ান,/ভাবিবার অবসর পায় সেকি, প্রিয়া/রয়েছে দোহার মাঝে কত ব্যবধান !”
শ্রীদিলীপকুমার রায়ের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল পত্রাকারে প্রবন্ধ রচনা। বুদ্ধদেব বসুর প্রগতিতেও দেখা গেছে এই প্রবণতা। ছায়াবীথিতেও তিনি আবদুল কাদির (দিলরুবা—কাব্য) ও নাজিরুল ইসলামের (গল্প—সোনালী স্বপন) দুটি বইয়ের প্রাপ্তিসংবাদ জানানোচ্ছ্বলে ‘গদ্য ও পদ্য’ বিষয়ে গুরুতর আলোচনার সূত্রপাত করে কয়েক সংখ্যাব্যাপি চালিয়ে গিয়েছেন। কাজী আবদুল ওদুদ তাঁর কবিগুরু গ্যেটে রচনার কালে ছায়াবীথিতে অনেকগুলো পর্ব দিয়েছিলেন। এই লেখাগুলোও সম্ভবত অমিলানো। সমালোচকদের হাতে ডধৎঃযবৎ/ ডধৎঃযবৎ পত্রোপন্যাসখানি দেশে-বিদেশের পাঠকদের কাছে অপূর্ব সমাদর লাভ করেছিল। ছায়াবীথির পাতায় কবিগুরু গ্যেটের এতদ্বিষয়ক কয়েকটি অংশ ছাপা হয়। ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত তাঁর ‘সমাজ ও সাহিত্য’ বইয়ের সমালোচনা; ড. মুহম্মদ এনামুল হক ও আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ এর প্রবন্ধ—‘আরকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য’ (কয়েক সংখ্যায় ক্রমাগত) এবং আবদুল কাদিরের ‘সঙ্গীত-চর্চ্চা’ শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশের পর তার উপর বিতর্ক চলে ‘সঙ্গীতে শ্লীলতা’ নামে; আর অংশগ্রহণ করেন—আবদুল কাদির ছাড়াও কাজী আবদুল ওদুদ ও নাজিরুল ইসলাম। আবদুল কাদির তাঁর প্রিয় বিষয়—‘ছন্দজিজ্ঞাসা’ শিরোনামে প্রবন্ধ রচনা করেন। শাহেদুল্লাহ লেখেন গল্প—‘গৃহপালিত জীব’; সুধীরকুমার মুখোপাধ্যায়ও গল্প লেখেন—‘আকাশ-কুসুম’; বন্দে আলী মিয়ার কবিতা—সোনালি ফাগুন দিনে; মোহাম্মদ আজরফ এমএর প্রবন্ধ—‘ধর্ম্ম ও নৈতিকতা’; মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন এমএ পল্লীগাঁথা সংগ্রহ করে ভূমিকাসহ প্রকাশ করেন—‘মইষাল বন্ধু’ নামে।
ছায়াবীথির সাইজ চতুরঙ্গের মতো। এক কলামে সুন্দর ছাপায় দৃষ্টি আকর্ষণের ক্ষমতা রাখে এর শিরোনামগুলোও। ঢাকার নারায়ণগঞ্জ থেকে একই সময়ে প্রকাশিত ‘সবুজ বাঙলা’র ১ বর্ষ ১ সংখ্যা বৈশাখ ১৩৪১ এ ছায়াবীথির বিজ্ঞাপনটির ভাষা ছিল নিম্নরূপ :
‘ছায়াবীথি। সচিত্র মাসিক পত্রিকা। আপনার সবচেয়ে প্রিয় কবি, ঔপন্যাসিক ও সাহিত্যিকগণের রচনা পড়িবার পিপাসা একমাত্র ছায়াবীথি পাঠেই নিবৃত্ত হইতে পারে। বাংলা মাসিক পত্রিকাগুলির ভিতরে ছায়াবীথি ইতিমধ্যেই একটি শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে। ছায়াবীথির বিশেষত্ব অতি আধুনিক সাহিত্য—বর্তমান দুনিয়ার আর্থিক ও সামাজিক সমস্যার আলোচনা এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বি শিল্পীর আঁকা ছবি। বার্ষিক চার টাকা আট আনা। অথবা ষান্মাসিক দুই টাকা চার আনা ব্যয়ে…, সম্পাদক নাজিরুল ইসলাম এমএবিটি, এফআরইকনএস। অফিস ৭৯/১, লোয়ার সার্কুলার রোড, ইন্টালী, পোঃ কলিকাতা। বৈশাখ হইতে ছায়াবীথি সম্পূর্ণ নূতন রূপ লইয়া বাহির হইতেছে।”
‘ছায়াবীথি’ প্রথমে ২৯ নং কালিদাস সিংহের লেন, কলকাতা ফিনিক্স প্রেস থেকে এন. ইসলাম দ্বারা মুদ্রিত ও ৭৯/১ লোয়ার সার্কুলার রোড থেকে এন. ইসলাম দ্বারা প্রকাশিত হবার তথ্য আছে। দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৩৪১ প্রকাশিত হয় দি এলায়েন্স প্রেস, ৬৩ বহুবাজার স্ট্রীট, কলকাতা থেকে মুদ্রিত হয়ে এবং প্রকাশিত হয় ৭৯/৩ বি লোয়ার সার্কুলার রোড থেকে। অতএব ঠিকানা বারে বারে পরিবর্তিত হয়েছে।
তবে মুদ্রণ সৌকর্য ও মান ক্ষুণ্ন হয়নি। সাহিত্যালোচনায় এবং পত্রিকা প্রকাশে সম্পাদক মৌলিকত্ব দেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন। পাকিস্তান আন্দোলনের তীব্রতা সুফিয়ানের চিন্তাধারাও পাল্টে দিয়েছিল। কিন্তু ছায়াবীথি একটি উদার, প্রগতিশীল গান্ধীবাদী পত্রিকা হিসেবে পরিচিত ছিল সে সময়ে। স্বরাজের প্রচারণাও তাঁদের পত্রিকায় রয়েছে। গান্ধীর মতাদর্শের প্রচারণা, স্বরাজ ও ইংরাজের শাসনব্যবস্থা ও গান্ধী-আরউইন চুক্তির সমালোচনা, নৈতিকতা, ধর্মদর্শন আর সাহিত্যশিল্পের প্রগতিশীল ধারার ছায়াপাত ছায়াবীথির পৃষ্ঠার ঝলকিত সৌকর্য সকলকে চমকিত ও আনন্দিত করবে নিঃসন্দেহে।
ইসরাইল খান, প্রাবন্ধিক ও গবেষক