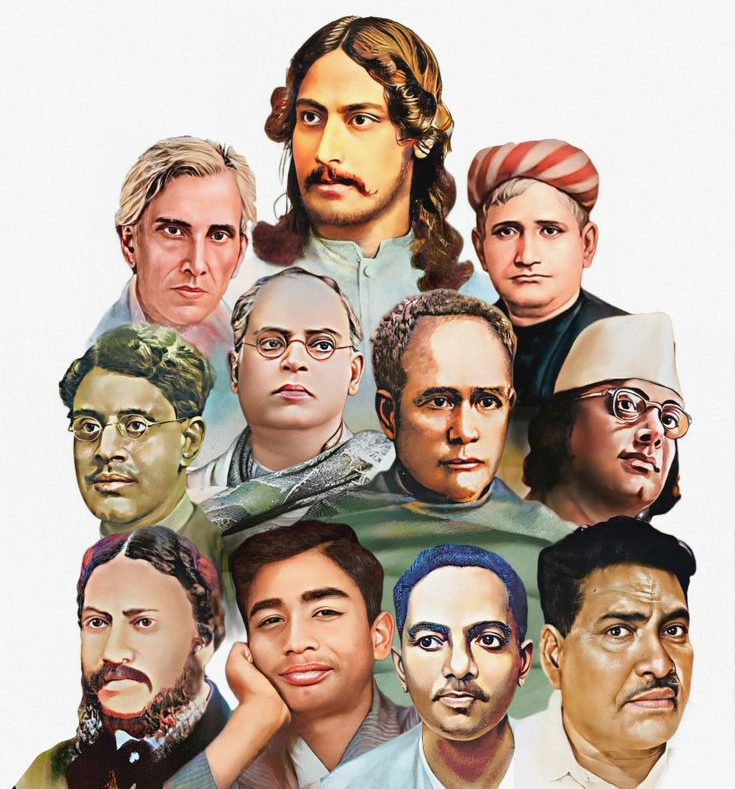ড. আহমেদ মাওলা
‘বাংলাদেশের সাহিত্য’ কথাটি আগে পরিষ্কার করে নিতে চাই। সাতচল্লিশে দেশভাগের পর বায়ান্ন’র ঘটনাবহুল সময়ের পটভূমি এবং একাত্তরে স্বাধীনতা অর্জনের পর অর্ধশত বছর অতিক্রম করছে বাংলাদেশ। এই সময়ের প্রেক্ষাপটে শনাক্তযোগ্য কিছু প্রবণতাকে চিহ্নিত করে আমরা বলতে চাই,বাঙালির জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাস ও জাতীয়তাবাদী তাত্ত্বিক পটভূমিকে কেন্দ্র করেই বাংলাদেশের সাহিত্যের বয়ান নির্মিত হয়েছে। ভাষাকেন্দ্রিক সৃষ্টিশীলতার মূল উপাদানকে বিবেচনা করে ‘বাংলাদেশের সাহিত্য’ কথাটার একটা সংহতরূপ দাঁড় করানো যায়। যদিও বাংলাদেশ কেবল বাঙালির রাষ্ট্র নয়, অন্যান্য ভাষাভাষি ক্ষুদ্র নৃগোষ্টী বহুকাল ধরে এদেশে বসবাস করছে। বাংলাদেশের সংবিধানে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে প্রধান করা হলেও অন্য ভাষার জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব ও অংশগ্রহণে গড়ে ওঠা সাহিত্য-সংস্কৃতি এই ধারণার মধ্যে থাকা জরুরি। দেশ বিভাগের পর থেকে একাত্তর পর্যন্ত বাংলাদেশের সাহিত্য বিকশিত হয়েছে মূলত বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধারণাকে কেন্দ্র করে। জাতীয়তাবাদী এই ধারণা উনিশ শতকে কলকাতা উৎপাদিত সাহিত্য-সংস্কৃতি দ্বারায় আরোপিত ছিল। কারণ তৎকালীন কলকাতায় উৎপাদিত বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধারণাকে উচ্চবর্ণ ও ভদ্রলোকশ্রেণির বাইরে ভাবা যায় না। সেই সাথে ছিল ঔপনিবেশিক আনুগত্য ও আধুনিকতার দাসত্ব।
শওকত ওসমান, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, বদরুদ্দীন উমর, শহীদুল্লা কায়সার, শামসুর রাহমান, শওকত আলী, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, হাসান আজিজুল হক, আহমদ রফিক, আনিসুজ্জামান, সৈয়দ শামসুল হক, মাহমুদুল হক, রফিক আজাদ, নির্মলেন্দু গুণ, ,যতীন সরকার, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আবদুল মান্নান সৈয়দ, হুমাযূন আজাদ প্রমুখ ইউরো-আধুনিকতাবাদী ও জাতীয়তাবাদী ধারা নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বদরুদ্দীন উমর এবং সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে পূর্ববাংলার সমাজ-ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। সেটা যতটা না পার্টিগত, তার চেয়ে বেশি আদর্শিক জায়গা থেকে করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের পর দেশজ ভিত্তিভূমির দিকে ফিরে তাকানোর একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। আহমদ ছফা, সেলিম আল দীন, রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, শহীদুল জহির প্রমুখ ইউরো-আধুনিকতার মোকাবেলায় কিছুটা তৎপর হতে দেখা যায়। অবশ্যই এটা নয় যে, এরা সাংগঠনিক শক্তি নিয়ে সম্মিলিতভাবে তৎপরতা চালিয়েছেন। তাদের কাজকে সরাসরি চিনুয়া আচেবের থিং ফল এ্যাপার্ট বা নগুগি ওয়াথিওঙ্গোর কাজের মতো বি-উপনিবেশিক বলে চিহ্নিত করা যাবে না। সত্তর-আশি-নব্বইয়ের দশকে বাংলাদেশের সাহিত্যের আত্মবিচার শুরু হয়। রাষ্ট্রীয় ক্যু, হত্যাকা-,সামরিক শাসন,সাম্প্রদায়িক খা-ব দাহন,বিচারহীনতা,গণতান্ত্রিক চেতনা অবলুপ্তি, সর্বাস্তরে দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়ন, এসব সমাজ-রাষ্ট্রকে দূষিত-দুরগন্ধময় করে তোলে। সমাজ ও রাজনীতির রন্দ্রে রন্দ্রে ঢুকে পড়া এসব পতন-পচনকে খুলেমেলে সাহিত্যে তুলে ধরেছেন মঈনুল আহসান সাবের, মঞ্জু সরকার, হরিপদ দত্ত, আহমদ বশীর, মামুন হুসাইন,ওয়াসি আহমেদ, ইমতিয়ার শামীম, তারেক খান, জাকির তালুকদার প্রমুখ কিন্তু অধিকাংশ লেখকই বাস্তবতাকে এড়িয়ে পদ-পুরস্কারকে সামনে রেখে, শাসকগোষ্ঠীর অনুকূলে কেচ্ছা-কাহিনি ফেঁদেছেন। সমান্তরালভাবে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা,মণিপুরি প্রভৃতি কবিতার একটা ক্ষীণধারা বহমান। মনে পড়ে, অনেক আগে আখরুজ্জামান ইলিয়াস আক্ষেপ করে লিখেছিলেন ‘চাকমা ভাষার উপন্যাস চাই’। সেই চাওয়া আজো পুরণ হলো না। আশি-নব্বই দশকে তাত্ত্বিকতার নামে সাহিত্যে আধার ও আশ্রয় হয়ে উঠেছিল লিটল ম্যাগাজিন। উত্তরাধুনিক, উত্তর-উপনিবেশিক চিন্তার আন্দোলন, স্বাদেশীকতা ও বৈশ্বিকতাকে কেউ কেউ বুঝতে চাইলেন লাতিনীয়-ইজম ও ইউরোপীয় নন্দনতত্ত্বের আচ্ছাদনে। লৈঙ্গিক রাজনীতিও চোখে পড়ে,সুফিয়া কামাল, সেলিনা হোসেন, তসলিমা নাসরিন, নাসরীন জাহান, আকিমুন রহমান, সালমা বাণী প্রমুখ নারী-পুরুষের অসমতা, পুরুষের আধিপত্য, নারী ধর্ষণ-নিপীড়ন নিয়ে প্রতিবাদী চেতনার বিস্তার ঘটিয়েছেন। আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগে সাহিত্যের নতুন পলল মাটির বিস্তার করতে তৎপর এবং বিউপনিবেশিক চিন্তার স্ফূরণ দেখা যাচ্ছে- মুজিব ইরম, ব্রাত্য রাইসু, শামীম রেজা, টোকন ঠাকুর, জফির সেতু , আহমাদ মোস্তাফা কামাল, প্রশান্ত মৃধা, রাখাল রাহা, তারেক খান,মাহবুব মোর্শেদ, মোজাফফর হোসেন,স্বকৃত নোমান, প্রমুখের লেখায়। আমাদের এখানে জনপ্রিয় সাহিত্যকে সন্দেহের চোখে দেখে এক ধরনের উপেক্ষা করা হয়েছে কিন্তু জনপ্রিয়তার বাস্তবতাকে কেউ তত্ত্ব-তালাশ করে দেখতে চায়নি। হুমায়ূন আহমেদ, ইমদাদুল হক মিলন, মঈনুল আহসান সাবের, মোহিত কামাল, সাহাদাত হোসাইন বইমেলার বেস্ট সেলারের তালিকায় থাকাটা কেবলই বেহুদা? এর পেছনে সোশ্যিয়ো-সাইকোলোজিক্যাল কোনো কারণ নেই? সমালোচনা-সাহিত্যের কোনো রীতি বা ঘরনা কিংবা তত্ত্বচিন্তার আলোকে সাহিত্য-পাঠের ঐতিহ্য এখানে গড়ে ওঠেনি। প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার হাল-হাকিকত কম-বেশি সবার জানা। উদ্ধৃতিসর্বস্ব,অনুসন্ধানহীন নিষ্প্রভ, চর্বিতচর্বণ ছাড়া কিছুই নেই। একাডেমিক আঙিনা বাইরে বরং চিৎ-চমক, কার্যকর গদ্য চোখে পড়ে। আবদুল মান্নান সৈয়দ, হুমায়ূন আজাদ মূলত ইউরো-আধুনিকতাবাদী ধরার সমালোচক। হাল আমলে ফরহাদ মজহার, সলিমুল্লাহ খান, আজফার হোসেন, সালাহউদ্দিন আইয়ূব, আহমেদ মাওলা, সৈয়দ ইকবাল,সুমন রহমান, মোহাম্মদ আজম, সুমন সাজ্জাদ, ফারুক ওয়াসিফ, মানস চৌধুরী, জগলুল আসাদ, কুদরত-ই-হুদা.ফয়েজ আলম, ফখরুল চৌধুরী প্রমুখ সোশ্যিয়ো-কালচারাল, বি-উপনিবেশিক দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্য-পাঠ ও বিশ্লেষণের ধারা গড়ে তুলতে তৎপর রয়েছেন।
ভূখ-গতভাবে দেশ স্বাধীন হলেও আমরা মূলত ঔপনিবেশিক বাস্তবতার মধ্যেই বসবাস করছি। আমাদের সমাজ-সংস্কৃতি ও মনোজগতের মধ্যে আজো ঔপনিবেশিকতার প্রবল প্রতাপ বিরাজমান। তিন তরফ থেকে বাংলাদেশ অঞ্চল ঔপনিবেশিকতার শিকার হয়েছে। প্রথমত ইংরেজ কলোনিয়াল সূত্রে, দ্বিতীয়বার হয়েছে উনিশ শতকে কলকাতা উৎপাদিত
সাহিত্য-সংস্কৃতি দ্বারা, তৃতীয়বার দেশভাগের পর পাকিস্তানি কর্তৃত্ববাদী শাসনের দ্বারা। সঙ্গত কারণেই বাঙালি মুসলমান পাকিস্তান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ছিল। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাঙালি জাতীয়তাবাদী জাগরণ শুরু হয় কিন্তু দুঃখজনকভাবে সত্য, জাতীয়তাবাদী ধারণা এবং অপরাপর চিন্তাচেতনার প্রশ্নে ঢাকার মানুষরা কলকাতার দিকে ফিরে তাকিয়েছে। ফলে পঞ্চাশ,ষাট এমনকি স্বাধীনতা-উত্তরকালেও ঢাকার চিন্তার জগত, সাহিত্য-শিল্পের জগত কলকাতার অনুকরণে,অনুসরণে, আরোপনের মধ্যে ডুবে আছে। সেই মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবগুলো চিহ্নিত করা ও সে সম্পর্কে সতর্ক হওয়ার কৌশলী তৎপরতার নামই হচ্ছে ‘উত্তর-উপনিবেশিকতাবাদ’। যে চাবি শব্দের উপর দাঁড়িয়ে ঔপনিবেশিক শাসনের জোয়াল আমরা কাঁধে বয়ে বেড়াচ্ছি, তার নাম ‘আধুনিকতা’। আমরা বলছি ইউরো-আধুনিকতা। নামান্তরে তা সা¤্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ, এককথায় ইউরোসেন্টিসিজম। আমরা তাকেই আঁকড়ে ধরে আছি। সেই এক অদৃশ্য শেকল।
ইতিহাস মোটেই অতীতের বিষয় নয়, বর্তমানকে বোঝা এবং চর্চার নামই ইতিহাসের সত্যিকার পাঠ। আন্তোনিও গ্রামশির ‘সাবটার্ন শ্রেণিসমূহ’ ধারণা থেকে রণজিৎ গুহ, গায়ত্রী স্পিভাক, গৌতম ভদ্র,দীপেশ চক্রর্তী, পার্থ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের নেতৃত্বে একদল ভারতীয় ভাবুক রাজ-রাজাদের ইতিহাসের বিকল্প ‘নি¤œবর্গের মানুষের ইতিহাস’ প্রস্তাব করেছেন। সাবলটার্ন স্টাডিজের প্রথম খ- ১৯৮২ সালে প্রকাশিত হওয়ার পর ইতিহাস ধরণার চমক সৃষ্টি হয়। ভারতবর্ষে ইতিহাস বলতে আমরা যা পড়ি, তা আসলে ঔপনিবেশিক প্রভুশক্তির স্তাবকতা ছাড়া কিছু নয়। সেই ‘মাইন্ডসেট’ থেকে বেরিয়ে আসার তাড়নাই আমাকে এই গ্রন্থের লেখাগুলো লিখতে উৎসাহ যুগিয়েছে।
দশকওয়ারি সাহিত্য বিবেচনার একটা প্রচল রীতি বদ্ধদেব বসু থেকেএকাডেমিক আঙিনায় বহুদিন ধরে মান্যতা পেয়ে আসছে। একাডেমিক সন্দর্ভ রচনার প্রয়োজনে প্রবহমানকাল থেকে একটি নির্দিষ্ট সময়কে বেছে নেয়া হয়ত অসঙ্গত নয় কিন্তু দশকওয়ারি সাহিত্য বিবেচনার ভালো-মন্দ নিয়ে নানা সমালোচনা রয়েছে। আমরা সেই আলাপে না গিয়ে বরং বলবো ‘বাংলাদেশের কথাসাহিত্য’ কথাটির মধ্যে ভূখ-গত একটি পরিচয়কে পাঠকের সামনে হাজির করা হয়েছে। সাহিত্যের এই স্বাতন্ত্র্য পরিচয় বাংলা ভাষার অন্য ভূগোল থেকে অবশ্যই পৃথক। বিশেষত, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ইত্যাদি ঘটনা এই অঞ্চলের সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতির চেহারা যেমন বদলে দিয়েছে, তেমনি আমাদের সাহিত্যের ভেতর ভুবনকেও আমূল বদলে দিয়েছে। স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের পরিচয় অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে গেলেও একথা অনস্বীকার্য যে,স্বতন্ত্র ভূখ-ের সাহিত্যিক অভিযাত্রা ভারত বিভাগ (১৯৪৭) পূর্বেই সূচিত হয়েছে। বিভাগোত্তর পূর্ব বাংলার রাজধানী সূত্রে ঢাকা হয়ে ওঠেছে বাংলাসাহিত্যের দ্বিতীয় রাজধানী। এখন অবশ্যই দ্বিধাহীনভাবে বলা যায়, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু ঢাকা। ‘সত্তর দশকের কথাসাহিত্য’ গ্রন্থে মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর সাহিত্যের নতুন এক মানচিত্র’কে হাজির করা হয়েছে।
প্রবহমান সময়ের বস্তুগত চেহারা কথাসাহিত্যে যতটা বাস্তাবিক করে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব অন্য কোনো শিল্প মাধ্যমে তা সম্ভব নয়। সন্দেহ নেই, মুক্তিযুদ্ধের অভিঘাতে বাংলাদেশের সমাজ সত্তার যে পরিবর্তন এসেছিল তার প্রথম ধাক্কা সব স্তরেই পড়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই কথাসাহিত্যেও পড়েছিল সময়ের চাপ, যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর সমাজ-পরিস্থিতি। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে, মুক্তিযুদ্ধের তাজা ঘটনাকে বিষয় করে রচিত হয়েছে অজ¯্র গল্পোপন্যাস কিন্তু সবই টলটলে, কাঁচা আবেগের। যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের জনজীবনে যে বিপুল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয়েছিল,তাকে সুনির্দিষ্ট বা শনাক্ত করার কাজটা হয়নি। তখনকার সদ্য স্বাধীনতার স্বাদ-গন্ধই ছিল আলাদা। আজকের সময়ের দূরত্বে বসে তা অনুভব করা যাবে না। শরনার্থীরা ফেরত আসছে দেশে নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ,অভাব-দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে, বিপ্লব-প্রতিবিপ্লবের দ্বন্দ্বে শুরু হয়েছে অবিনাশী আয়োজন। সশস্ত্র দুষ্কৃতিকারীদের লুণ্ঠন,ডাকাতিতে অস্থির,ভীত জনজীবন। গণতন্ত্র ভূলণ্ঠিত,বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করছে একদল বিপথগামী সামরিক কর্মকর্তা,অভ্যুত্থান পাল্টা অভ্যুত্থান, ক্যু, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পালাবদল,এই অরাজগকতার মধ্যে কেবল রাষ্ট্রীয় নীতি বদলেছে, তা নয়, মানুষের মনোজগতে বিশ্বাসের ফাটল ধরেছে,সামাজিক মূল্যবোধের ধ্বংস নেমেছে, ভয়বহ সংকটের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে মানুষকে। ভাষিক শিল্প হিসেবে কথাসাহিত্য সেই চিহ্ন,চারিত্র্যকে ধারণ করেছে, অবশ্য সবটুকু নয়, খ-িত ।
সত্তর দশকের কথাসাহিত্য আতিমাত্রায় রাজনীতি প্রবণ হয়ে উঠে,কারণ রাজনীতি ছিল বিশৃঙ্খল, মানুষের আকাক্সক্ষ ছিল তুঙ্গে, চাহিদা ছিল বিপুল। ষাটের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর নানান ধরনের চর্চা তখনো অব্যাহত ছিল, সেই সময়টি ধরার প্রয়োজনে আমাদের কথাসাহিত্যিকরা যে জনপ্রিয়ধারায় লিখেছেন, এতে বিস্মিত হওয়ার কারণ নেই, এটা দোষেরও কিছু নয়। তিন ধরনের দৃষ্টি এক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়।
১.মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা সরাসরি কথাসাহিত্যের বিষয় হয়ে উঠে। হানাদার বাহিনীর হত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণ, নৃশংসতার বর্ণনা ক্রাইম স্টোরি লেখার মতো কথাসাহিত্যিকরা লিখেছেন, যা পড়ে মনে হয়, লেখকরা যা দেখেছেন তা সবটুকুই লিখে ফেলেছেন। মুক্তিযুদ্ধের রক্তাক্ত অভিজ্ঞতা,আত্মত্যাগ চেতনা হিসেবে কথাসাহিত্যে পরিচর্যা পায়নি। বিষয় ও চেতনার মধ্যে সূক্ষ্ম দার্শনিক যে পার্থক্য ঘটে গেছে, সে জন্যই ‘মুক্তিযুদ্ধের সাহিত্য’ নামে রচিত গল্প-উপন্যাস যথেষ্ট আবেগ ছড়ালেও শিল্পের বিচারে মহৎ,বৃহৎ, চিরায়ত হওয়ার ত্রুটি থেকে মুক্ত হতে পারেনি।
যেমন সৈয়দ শামসুল হকের ‘নীল দংশন’ ‘নিষিদ্ধ লোবান’ উপন্যাস। ‘নীল দংশন’ উপন্যাসে বিলকিসকে পাকিস্তানী মেজর যে প্রক্রিয়ায় ধর্ষণ করে, তা পড়লে মনে হয় হানাদার কাহিনীর হাতে আমাদের বীরঙ্গনারা যাতটুকু না ধর্ষিতা হয়েছে তার চেয়ে বেশি ধর্ষণ করেছেন লেখক কলমের ডগা দিয়ে। তাঁর ‘নিষিদ্ধ লোবান’ উপন্যাসের কাজী নজরুল ইসলাম চরিত্রটিও আরোপিত। অনুরূপ উপন্যাস শওকত ওসমানের ‘নেকড়ে অরণ্য’ ইমদাদুল হক মিলনের ‘ঘেরাও’।
২. মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ বিবরণ, বর্ণনা, আক্রান্ত স্বদেশের প্রতি প্রেম,দায়বদ্ধতা, পাকিস্তানি হানাদার ও তাদের দোসরদের পৈশাচিকতার চিত্র নিখুঁতভাবে রূপায়িত আনেক উপন্যাসে। আনোয়ার পাশার ‘রাইফেল রোটি আওরাত’ এর সুদীপ্ত শাহীন, শকেত আলীর ‘যাত্রা’র রায়হান, শওকত ওসমানের ‘জাহান্নাম হইতে বিদায়’র গাজী রহমান, নিজেরাই পেশায় শিক্ষক এবং এরা সকলে আক্রান্ত শহর থেকে নিরাপদে চলে যাওয়ার পথে যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে, নৃশংসতা দেখে। আমজাদ হোসেনের ‘অবেলায় অসময়’র নৌকার যাত্রীরা নদী থেকে নদীতে ঘুরে বেড়ায় নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। রশীদ হাযদারের ‘খাঁচায়’ মধ্যবিত্ত, চাকুরে জীবনে ঢাকা শহরে দোতলা বাড়িতে বসে রেডিও শোনে, পাড়া থেকে পাকিস্তান বাহিনী মেয়ে তুলে নেয়ার খবর পায়, বোমার আতঙ্কে বাতি না জ্বালিয়ে অন্ধকারে থাকে, এটাতো খুব রিয়েল পিকচার। এসব উপন্যাসে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি একধরনের পক্ষপাত বা মমত্ববোধ কাজ করে সত্যি কিন্তু এই পক্ষপাত,বিশেষ কোনো দায় নেয় না,দায়িত্ব বহন করে না। তাদের কাছে মুক্তিযুদ্ধ যেন উদ্দেশ্যহীন।
৩. স্বাধীনতা উত্তর বিলোড়িত সমাজের চিত্র-চারিত্র্য। ইমদাদুল হক মিলনের ‘কালোঘোড়া, ‘দ্বিতীয় পর্বের শুরু, হারুন হাবীবের ‘প্রিয়যোদ্ধা, প্রিয়তমা’, শহীদুল জহিরের ‘জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা’, নাসরীন জাহানের ‘যখন চারপাশের বাতিগুলো নিভে আসছে’ ইত্যাদি। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধকে বিষয় করে রচিত উপন্যাসে হচ্ছে মাহমুদুল হকের ‘জীবন আমার বোন’, রাবেয়া খাতুনের ‘ফেরারী সূর্য্য’, সেলিনা হোসেনের ‘হাঙর নদী’, গ্রেনেড’‘যুদ্ধ’ হুমায়ূন আহমেদের ‘১৯৭১,’ ‘সূর্য্যরে দিন’, ‘আগুনের পরশমনি’, রিজিয়া রহমানের ‘সূর্য সবুজ রক্ত’, ‘একটি ফুলের জন্য’, ‘হারুন ফেরেনি’, রাহাত খানের ‘ছায়া দম্পতি’, হাসনা আবদুল হইযের ‘তিমি’, শওকত আলীর ‘অবশেষে প্রপাত’, মাহবুব তালুকদারের ‘অপলাপ’, রাজিয়া খানের ‘হে মহাজীবন’, শহীদুল জহিরের ‘জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা’, ইমদাদুল হক মিলনের ‘কালো ঘোড়া,’ ‘দ্বিতীয় পর্বের শুরু’, মঞ্জু সরকারের উপন্যাস এবং মঈনুল আহসান সাবেরের ‘পাথর সময়’, ‘কবেজ লেঠেল’, ‘সতের বছর পর’ ইত্যাদি উপন্যাসে স্বাধীনতা উত্তর সমাজের রূপ বদলের চিত্র ফুটে উঠেছে।
মুক্তিযুদ্ধকে আমাদের কথাশিল্পীরা কিভাবে দেখেছেন? এই প্রশ্ন সামনে রেখে উপর্যুক্ত উপন্যাসগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায়, শ্রুতি ও স্মৃতি দিয়ে কাহিনি তৈরি করেছেন লেখকরা, সবই যেন বানিয়ে তোলা ঘটনার বিবরণ। আসলে সমাজ সত্তার গভীরে প্রোথিত চেতনার সঙ্গে শিল্পীর মনের বিশ্বাসের সমন্বয় না হলে কোনো শিল্প কর্মই মহৎ ও আয়ুষ্মান হতে পারে না। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে চেতনা পরিপ্লাবি উপন্যাস রচিত হয়নি, কারণ, লেখকদের যাঁরা সরাসরি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা প্রত্যক্ষঅভিজ্ঞতার বর্ণনা দিযেছেন কেবল, সেই বিবরণে বৃহত্তর চেতনার প্রতিফলন ঘটেনি, একধরনের আবেগ, উপভোগসর্বস্ব হয়ে উঠেছে। একথা ‘রাইফেল রোিিট আওয়ারাত’-এর সুদীপ্র শাহীন কিংবা ‘যাত্রা’র রায়হান মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বের আহ্বানেও সাড়া দেয় না, মনে সেজন্য গ্লাণিবোধ করেন কিন্তু নিজের স্ত্রী পুত্রকে নিয়ে নিরাপদে আশ্রয়ের সন্ধানে সে অগ্রসর হয়। ‘ব্যাপক সর্বনাশের মধ্যে নিক্ষিপ্ত অগণিত মানুষের ভেতরেও এই মধ্যবিত্ত নিঃসঙ্গ একাকী তার ‘খাঁচায়’, দুই ক্রমাগত সংকটের কেন্দ্র থেকে পলায়ন, যেমন ‘জাহান্নাম হইতে বিদায়’ এর গাজী রহমান, ‘যাত্রা’র রায়হান। মাহমুদুল হকের ‘জীবন আমার বোন’ এও একই সূত্রের উদভাসন চোখে পড়ে। এ উপন্যাসের নায়ক খোকা, যার ‘পলায়ন ছাড়া কোনো ভূমিকা নেই, তার কাছে প্রীতিলতা, মতিয়ুরের বাংলাদেশ হয়ে যায় একটা বাংলা মদের বোতল কিংবা ‘ঘুটঘুটে বেশ্যালয়’্ একধরনের যৌনতাড়িত, রোমান্টিক নাগরিক জীবনের যন্ত্রণাকে তুলে ধরেছেন লেখক। এ উপন্যাসের কেউ আবার যুদ্ধের কারণে বিবাহ স্থগিত হয়ে যায় বলে আফসোস করে। সেলিনা হোসেনের ‘হাঙর নদী গ্রেনেড’ এ হলদি গাঁ, বুড়ি চরিত্র, গ্রামীণ হলেও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে ন্ াবাংলাদেশের নিস্তরঙ্গ গ্রাম পরিবেশের জীবনে মুক্তিযুদ্ধ কীভাবে অভিঘাত এনেছিল , তার কাহিনি এ উপন্যাসে পাওয়া যায় কিন্তু তিনি যে গ্রামের বর্ণনা দেন ‘হলদি গাঁ’ তার নামটা পর্যন্ত কৃত্রিম বলে মনে হয়। বুড়ির চরিত্রও আগাগোড়া গ-িবদ্ধ, বড়ির আত্মোঃসর্গ, শত্রুর মুখে সন্তান ছুঁড়ে মারাকে মনে হয় অতি আবেগের উৎসারণ, সামগ্রিক চেতনায় জীবন্ত অনুভূতি নিয়ে হৃদয়ে দাগ কাটে না।
সত্তর দশকে এসে আমাদের কথাসাহিত্যে দু’টি ধারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে-
১.জনপ্রিয় ধারা। ২. সিরিয়াস বা মূলধারা। ‘জনপ্রিয় সাহিত্য’ এবং ‘কালজয়ী স্মরণীয় সাহিত্য’ এর মধ্যে পার্থক্য আসলে কী? একজন লেখক ‘জনপ্রিয়’ হন দুটি কারণে। এক. বড় লেখকদের সমৃদ্ধ উপলব্ধি জগৎ তাঁদের ভেতর থাকে না বলে। দুই. তাঁদের মধ্যে শিল্পের উচ্চতর সম্পন্নতা থাকে না বলে। অর্থাৎ জনপ্রিয় লেখকদের লেখা পড়তে সুখকর, পড়লে আনন্দ পাওয়া যায় কিন্তু তাঁদের লেখা অন্তঃসারশূন্য, জলো, স্থায়িত্ব বলে কিছু থাকে না। বিনোদনের মচমচে স্বাদ, যার অপ্রতিহত আকর্ষণে পাঠককে তাঁর কাছে টেনে নিয়ে যায়, ঝাঁজালো সম্মোহনে আচ্ছন্ন করে রাখে। রোমান্টিক প্রেম, চটুল গল্পের ফাঁদে ফেলে বা সুড়সুডি লাগা যৌনতা প্রলেপ দিয়েও কেউ কেউ সাহিত্যের বাজারে জনপ্রিয় হতে পারেন।
অন্যদিকে নন্দনতাত্ত্বিকরা শিল্পের যে দেহকান্তির কথা কল্পনা করেছেন, তার নাম হচ্ছে অনিন্দ্য সুন্দর। জীবন-উপলব্ধি, অন্তর্দৃষ্টি, শিল্পবোধ, যা পাঠকের হৃদয়ে আনন্দ-আবেগ জাগিয়ে তুলতে না পারলে, তা শিল্পের পর্যায়ে উঠে আসে না। যে নয়টি রসের কথা নন্দনতাত্ত্বিকরা বলেছেন, কোনো লেখার মধ্যে যে কোনো একটি একাধিক রস সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়ে পাঠকের হৃদয়ে আনন্দময় অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে পারলেই তা শিল্প হিসেবে উত্তীর্ণ হয়। শিল্পের সেই সোনালি দরজা, যার ভেতর দিয়ে শিল্পী তার বক্তব্যকে পাঠকের হৃদয়ে সঞ্চারিত করে দিতে পারেন, রসসিক্ত করে পরিবেশন করতে পারেন, তিনিই শিল্পী। শেক্্সপিয়ার, সফোক্লিস, ইবসেন, তলস্তয়, দস্তয়েভস্কি, গাব্রিয়েল মার্কেজ, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, মানিক, বিভূতি, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ শিল্পের সেই উঁচু শিখরকে স্পর্শ করতে পেরেছেন বলেই তাঁরা আজ পর্যন্ত মানুষের কাছে নন্দিত, সম্মোহিত। এর কারণ তাঁদের লেখার ভেতরকার অসাধারণ শিল্প শক্তি, যা চিরায়ত, কালোত্তীর্ণ। শিল্পে যার নাম লাবণ্য, দ্যুতিময় বৈভব বলে।
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ তাঁর ‘জনপ্রিয় লেখকরা কি অলেখক?’ প্রবন্ধে লিখেছেনÑ ‘তাহলে জনপ্রিয়তার গুণ আর লেখকের গুণ আলাদা?’ জনপ্রিয়তা দোষ না গুণ? ‘জনপ্রিয়’ শব্দটি দ্ব্যর্থবোধক এবং এই দ্ব্যর্থতা পরস্পরবিরোধী। এক অর্থে সস্তা নি¤œরুচির পরিচায়ক, অন্য অর্থে পাঠকনন্দিত।(আবু সায়ীদ : ২০১৩, পৃ: ১৮) হুমায়ূন আজাদ একবার পত্রিকায় সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘তের থেকে ত্রিশ বছরের অপরিণত কিশোর-তরুণ-তরুণীরাই হুমায়ূন আহমেদের প্রধান পাঠক। তারা মাতালের মতো, পাগলের মতো, উন্মাদ মৌমাছিদের মতো বইমেলায় ছুটে যায়। দীর্ঘ, লাইন ধরে অটোগ্রাফ নেয়, হুমায়ূন আহমেদের বই কেনে।’ এই মাতাল পাঠকদের একবার প্রশ্ন করা হয়েছিলÑ ‘তোমরা হমায়ূন আহমেদের বই পড় কেন? উত্তরে ওই তরুণ, বিপুল পাঠকগোষ্ঠী জবাব দিয়েছিলÑ ‘তাঁর লেখা ভালো লাগে। পড়লে আনন্দ পাই। জীবন নতুনভাবে তুলে ধরে আমাদের সামনে। জীবনকে নতুন করে দেখায়। আমাদেও মনকে প্রসারিত করে। মনকে বড় করে।’ তরুণ-তরুণীদের উত্তরের মধ্যে হুমায়ূন আহমেদের লেখার একটা সরল মূল্যায়ন আছে। যদিও,হুমায়ূন আহমেদকে ‘বাজারি লেখক’ ‘তুচ্ছ লেখক’ বলে সমকালে অনেকে তাঁকে নিন্দা-মন্দ করেছেন। হুমায়ূন আহমেদ তাঁর ‘ফাউন্টেনপেন’ (২০১১) আত্মজীবনীমূলক রচনায় জুতসই জবাব দিয়ে গেছেনÑ
‘বাজারি লেখক মানে তুচ্ছ লেখক। তেল-সাবান-পেঁয়াজ-কাঁচা মরিচ বিক্রেতা টাইপ লেখক। এদের বই বাজারে পাওয়া যায় বলেও বাজারি। যাদের বই বাজারে পাওয়া যায় না, তাদের বাড়িতে কার্টন ভর্তি থাকে, তারা মহান লেখক, মুক্তবুদ্ধির লেখক, কমিটেড লেখক, সত্যসন্ধানী লেখক। তাঁদের বেশির ভাগের ধারণা, তাঁরা কালজয় করে ফেলেছেন। এঁরা বাজারি লেখকদের কঠিন আক্রমণ করতে ভালোবাসেন।…
কালজয়ী এইসব মহান লেখকের সঙ্গে মাঝে মাঝে আমার দেখা হয়ে যায়। এমন একজনের সঙ্গে কথোপকথনের নমুনাÑ
কালজয়ী : কেমন আছেন?
আমি : জি ভালো।
কালজয়ী : ইদানিং কিছু কি লিখছেন?
আমি : একটা সস্তা প্রেমের উপন্যাস লেখার চেষ্টা করছি।
যতটা সস্তা হওয়া দরকার ততটা সস্তা হচ্ছে না বলে অস্বস্তিতে আছি। আপনার দোয়া চাই যেন আরেকটা সস্তা লিখতে পারি।
কালজয়ী : (গম্ভীর)
আমি : আপনি কি মহান কোনো লেখায় হাত দিয়েছেন?
আমার মনে হয় ‘জনপ্রিয়’ শব্দর্টি ভুলভাবে প্রয়োগ করা হয়। এক বিচিত্র কারণে বাংলাদেশ অঞ্চলের মানুষেরা জনপ্রিয়তাকে সন্দেহের চোখে দেখে। আসলে হুমায়ূন আহমেদ ছিলেন মূলত পাঠকপ্রিয় লেখক। তাঁর লেখায় যদি পাঠকদের ‘প্রিয়’ কিছু না থাকতো তবে মানুষ নিজের পকেটের নগদ টাকা খরচ করে তাঁর বই কিনবে? তিনি ব্যাপক পাঠক চিত্তকে জয় করে নিয়েছেন তাঁর লেখার অসাধারণ প্রসাদগুণ দিয়ে, নিজস্ব শ্রম, সাধনা ও নিষ্ঠা দিয়ে অর্জন করেছেন সাফল্যের অভিজ্ঞান পত্র।
হুমায়ূন আহমেদ, ইমদাদুল হক মিলন, মঈনুল আহসান সাবের প্রমুখ জনপ্রিয় ধারায় এবং লেখালেখির ক্ষেত্রে অধিক তৎপর। এঁদের বিষয় মূলত নতুন গড়ে ওঠা মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রাত্যহিক জীবন-যাপন, আশা-আকাক্সক্ষা, স্বপ্ন, প্রেম-প্রণয়। মধ্যবিত্তে জীবনের গভীরে যে স্বার্থপরতা, নোংরামি ও নষ্টামি, চালাকি, বদমায়েশি, সাধ্যে অতীত স্বপ্ন নিয়ে যে মধ্যবিত্ত সমূহ সর্বনাশের দিকে এগিযে যাচ্ছে, তার স্বরূপ উন্মোচন কিংবা কোনো গভীরতর জীবনবীক্ষা তাঁদের রচনায় সেই চোখে পড়ে না। রচনার শিল্পমান, প্রকরণ-পরিচর্যা বিষয়েও তাঁরা উদাসীন,অমনোযোগী? উপর্যুক্ত লেখকদের শক্তি সন্দেহাতীত প্রতীতি থাকা সত্ত্বেও আমাদের ভাবতে কষ্ট হয় যে, অবলোকনের অনেকান্তিক দৃষ্টি, জীবনের গভীরতর তাৎপর্য রূপকল্প নির্মাণ, স্বপ্ন ও চেতনার সৃষ্টির ব্যপারে উদাসীন। তাদের বেশ কয়েকটি রচনায় যে সেই স্বাক্ষর নেই, এমন নয়। যেমন হুমায়ূন আহমেদের ‘নন্দিত নরকে,’ ‘ময়ূরাক্ষী,’ ‘এই বসন্তে,’ ‘আগুনের পরশমনি,’ ‘অচিনপুর,’ ‘ফেরা,’ ‘জোছনা ও জননীর গল্প,’ ‘অনিল বাগচীর একদিন,’ ‘নির্বাসন’, ইদাদুল হক মিলনের ‘পরাধীনতা,’ ‘কালাকাল,’‘নদী উপাখ্যান,’ ‘ভূমিপুত্র,’ ‘নূরজাহান,’ ‘দ্বিতীয়পর্বের শুরু,’ ‘বনমানুষ,’ ‘যাবজ্জীবন’, মঈনুল আহসান সাবেরের ‘পাথর সময়,’ ‘কবেজ লেঠেল,’ ‘ঠাট্টা,’ ‘সতেরো বছর পর,’ ‘যে কারণে আব্দুল জলিল মারা গেল’, ‘আমাদের খঞ্জনপুর,‘ ‘এই দেখা যায় বাংলাদেশ’ ইত্যাদি। উল্লিখিত উপন্যাসগুলোর মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ এবং তার পরবর্তী আর্থসামাজিক জীবনের ভাঙচুর, রাজনৈতিক পালাবদলের উদ্ভাসন লক্ষ্য করা যায়।
মূলধারা বা সিরিয়াস ধারায় বুলবুল চৌধুরীর, কহ কামিনী (১৯৯৫), পাপপুণ্যি (১৯৯৫), জলটুঙ্গি (১৯৯৫), দখিনা বাও (২০১১), ঘর আড়ি (১৯৯৬), দম্পতি (১৯৯৭), অপরূপ বিল ঝির নদী (১৯৯৮), অচিনে আঁচড়ি (২০০৩), মরম বাখানি (২০০৭), তিয়াসের লেখন (২০১৬), এই ঘরে লক্ষ্মী থাকে (২০১৫) মঞ্জু সরকারের, নগ্ন আগন্তুক (১৯৮৬), প্রতিমা উপাখ্যান (১৯৯২), দাড়াবার জায়গা (১৯৯৪), আবাসভূমি (১৯৯৪), বরপুত্র (২০১০), আহমদ বশীরের অবাস্তব বাস্তব (২০১৬), তিথিডোর: মুক্তিযুদ্ধের একটা উপন্যাস হতে পারতো (২০১৭), স্বাধীনতার পরের এক পরাধীনতা (২০১৮), মুদ্রারাক্ষস (২০২১), হরিপদ দত্তের একাত্তরের ধ্রুপদী (১৯৯৪), অজগর (১৯৯৬), ঈশানে আগ্নিদাহ (১৯৯৫), যুদ্ধ অমানিশার গণকবর ২০১০), চিম্বুক পাহাড়ের জাতক (২০১২) দ্রাবিড় গ্রাম (২০০৯), অন্ধকূপে জন্মোৎসব (২০০৬), তাপস মজুমদারের শব্দকরের আকাশবাজি (২০১০), আশালতা ও ম্যাজেশিয়ান (২০১৫), আবু সাঈদ জুবেরী, বারেক আবদুল্লাহ প্রমুখ ষাটের নির্মিত জমিনে সফল ফসল ফলিয়েছেন। এঁরা হাসান আজিজুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ঘরানার যোগ্য উত্তরাধিকার। এঁরা জীবন দৃষ্টিতে বাস্তববাদী, কিন্তু প্রকরণ পরিচর্যায় উদাসীন। কয়েকটি দুঃখ-যন্ত্রণার কথা, দারিদ্র্যের কথা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বললেই শিল্পের দায় মেটে না বরং বিষয়, ভাষা, রচনা, কৌশলে সর্বজ্ঞ দৃষ্টি থাকা দরকার। মুক্তিযুদ্ধকে বিষয় করে যাঁরা গল্পোপন্যাস লিখেছেন, তাদের প্রধান প্রবণতা ছিল-হানাদারদের অত্যাচার, জুলুম নির্যাতন, ধর্ষণ ইত্যাদি নারকীয় ঘটনা অতি আগ্রহের সঙ্গে বর্ণনা। তাঁরা মনে করেছেন, এর মাধ্যমে হানাদারদের প্রতি সাধারণ মানুষের মনে অধিক ঘৃণা জন্মাবে এবং মানুষের আত্মত্যাগের চিত্র মহীয়ান হয়ে উঠবে। প্রশংসা করার অনেক বাস্তব চিত্র অনেকের রচনায় আছে তবু নির্লিপ্ত নৈর্ব্যক্তিকতা ও জীবন দৃষ্টির অভাবে কোনো রচনা শিল্প স্তরে পৌঁছে নি।
স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পর আজো রাজনৈতিক মঞ্চে শুনি ‘মুক্তিযুদ্ধের সুফল ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে’ অর্থাৎ আমাদের জাতীয় জীবনেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতিফলন ঘটেনি। মীমাংসা হয় নি মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষ বিপক্ষের চেতনার পরিপ্লাবি উচ্চারণ দূরাশা মাত্র।
মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আজ একেক দলের কাছে একেক রকম। তবে এ কথা ঠিক যে, জাতি হিসেবে বাঙালির স্বাতন্ত্র্য চেতনা স্বাধিকার ও শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্যই সাধারণ মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পরবর্তীকালে মধ্যবিত্ত শ্রেণির স্বার্থপরতা, উচ্চাভিলাস, সেনা সদস্যদের রাষ্টীয় ক্ষমতা দখল, একাধিক অভ্যুত্থান, মুুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ভূলুন্ঠিত করেছে। সমাজ সত্তার এই বাস্তব কারণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আমাদের শিল্পীদের মনের গভীরে লালন ও পরিচর্যা হয় নি। এরকম প্রবোধ মেনে নিয়ে শান্ত¦না পাওয়া যায়, কিন্তু দায়িত্ব এড়ানো যায় না। মুক্তিযুদ্ধের গল্পোপন্যাসে যা পাই নি, তার বিবরণ দেয়া আমার অভিপ্রায় নয়, আমি বলতে চাচ্ছি মুক্তিযুদ্ধকে বিষয় করে রচিত গল্পোপন্যাসে আমাদের সমাজের কোন অবয়ব উৎকীর্ণ ? কী চেতনা কাজ করেছে লেখকদের মনে ? আমি দেখতে পাই মুক্তিযুদ্ধের এত বড় অভিঘাত আমাদের মননে কোনো মহৎ চেতনার সঞ্চার নেই, বৃহৎ জীবনাবেগের রূপায়ন নেই, গভীর শিল্পবোধের উদ্ভাস নেই। চেতনার বদলে এসেছে অপরিশ্রুত আবেগ, খ-িত জীবনচিত্র, মেধাহীন বাক্যের অপচয় ঘটেছে ব্যাপক হারে। এর কারণ, অধিকাংশ গল্পোপন্যাসেই রচিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পরে, ফলত সবই কাঁচা আবেগের উত্তাপে ধূমায়িত উল্লাশ আক্ষেপ, ঘৃণা ও প্রতিক্রয়ায় পর্যবসিত। মুক্তিযুদ্ধের পর, স্বাধীন বাংলাদেশের সমাজের তাৎপর্যময় কোনো রুপান্তর লক্ষ্য করা যায় নি। কিছু কিছু মূল্যবোধের ভাঙচুর ঘটেছে, কিছু কিছু সংস্কারেরও পরিবর্তন হয়েছে সত্যি কিন্তু যে চেতনায় ও আদর্শবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ মুক্তিযুদ্ধ করেছিল, অচিরেই তাদের মধ্যে নেমে আসে ব্যাপক হতাশা, সংক্রামক ব্যাধির মতো দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়ে সমাজের সর্বত্র্ বর্ণ চোরা সময়ের এই চিত্র ও চরিত্র্য আমাদের কথাসাহিত্যে পড়েছে। রাহাত খানের ‘ছায়া দম্পতি’ হাসনা আবদুল হইযের ‘তিমি’ শওকত আলীর ‘অবশেষে প্রপাত’ মাহবুব তালুকদারের ‘অপলাপ’ রাজিয়া খানের ‘হে মহাজীবন’,সেলিনা হোসেনের ‘পদশব্দ’ উপন্যাসে। রাজিয়া খানের নায়িকা দাম্পত্য জীবনে প্রবঞ্চিতা, কিন্তু পূর্ব প্রেমিকের সাথে বিবাহ বহির্ভূত দেহজ সম্পর্ক জেগে উঠতে তার মনে কোনো গ্লানি নেই, কেননা সেখানে শরীরের সাথে যোগসূত্র বেঁধে দেয় আত্মার জাগরণ। সেলিনা হোসেনের নায়িকা সালমা বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধু রকিবকে ভালোবেসেই দেহ দান করে। আত্মকেন্দ্রিক জনক-জননীর ¯েœহ বঞ্চিতা সালমা যদিও মা বাবার অজ্ঞাতেই রকিবকে বিয়ে করে শেষ পর্যন্ত, কিন্তু সে কিছুতেই সমাজের প্রথাগত নিয়মের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারে না। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের সমাজ জীবনে মূল্যবোধের এই ভাঙচুরের চিত্র, নৈতিক পতন স্খলনের ফলে যে সংকটের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয় মধ্যবিত্ত সমাজকে, তার ছবি ফুটে ওঠে শওকত আলীর ‘অবশেষে প্রপাত’ উপন্যাসে। মাহমুদুল হকের ‘অশরীরী’ উপন্যাসের তাহেরা অন্তঃসত্ত্বা জেনেও আম্বিয়া তাকে বিয়ে করে, যদিও অনাগত সন্তানের জনক সে নয়। আবার বশীর আল হেলালের ‘ঘৃতকুমারী’ তে দেখি দুর্নীতির দায়ে গ্রেফতারকৃত স্বামীর প্রতি ঘৃণায় স্ত্রী অন্য পুরুষের সাথে রাত্রিযাপনে ইতস্তত করছে না। কিন্তু সেও যখন তার ভুল বুঝতে পেরেছে, ফিরে এসেছে স্বামীর সংসারে, অনুতপ্ত, অপরাধী। স্বামী দাউদ এতো সহজে স্ত্রীকে গ্রহণ করতে চায়নি তবে দিলরুবার শীতল নিরাবেগ যুক্তির কাছে তাকে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে শেষ পর্যন্ত। এই মধ্যবিত্ত ঘরণী স্পষ্ট ভাষায় বলেছেÑ আমাকে যদি তোমার আর ভালো নাও লাগে তবু আমাকে তোমার স্ত্রী হয়ে থাকতে দিতে হবে। কারণ এই হচ্ছে সভ্য সমাজের নিয়ম।’ দাউদের বৃদ্ধা মা কিন্তু সেই নিয়ম মেনে নিতে পারেন নি। তিনি তখনি তার ছোট ছেলের বাসায় চলে যাওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে এবং দাউদ বাধা দেননি তাঁকে।’(আবু হেনা মোস্তাফা কামাল: কথা ও কবিতা, ঢাকা ১৯৮১ পৃ:১১৩) সত্তর দশকে আমাদের কথাসাহিত্যে এই বাস্তবমুখিতা প্রকাশ করতে গিয়ে উপন্যাস হয়ে পড়েছে শিল্পহীন বয়ান, কেবল অবক্ষয়ের প্রতিকারহীন বর্ণনা, বৈচিত্র্যহীন কাহিনির পুনরাবৃত্তি। সময়ের বাস্তব চিত্র হিসেবে এগুলোর মূল্য অনস্বীকার্য কিন্তু সময়ের দাবি পূরণ করলেও সত্তর দশকের উপন্যাসের গভীরতা কম। প্রকরণ পরিচর্যার নিরীক্ষাও এপর্বে লেখকদের রচনায় নেই।
বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের সহজতর একটা গদ্য ভাষা তৈরি হয়েছে। এখন এই সহজতর গদ্য ভাষা কাজে লাগিয়ে, গভীরতর জীবনবোধ, অবলোকনের অনেকান্তিক দৃষ্টির প্রতিভাবান, মেধাবী শিল্পীর অপেক্ষায়। জীবনার্থের শিল্প প্রতিমা নির্মাণই কথাসাহিত্যের আসল উদ্দেশ্য। লেখকের জীবনবোধ যতো গভীর ততোই তিনি নির্লিপ্তকে কণ্ঠহার করে জীবনের সারৎসার রূপন্বিত করতে পারেন। নির্লিপ্তির অর্থ একগাদা বাস্তবের সঞ্চয়ন নয়, ডিটেইলস্- এর তালিকা তৈরী নয়, নির্লিপ্তির অর্থ হচ্ছে গভীরতর জীবনবীক্ষা। নানাবিধ উপকরণের আশ্রয়ে একটি উপন্যাস বা গল্পের অবয়ব তৈরি হয়-প্লট, চরিত্র, সংলাপ, ভাষা- বয়ানভঙ্গি অনেক কিছু। কখনো মনে হতে পারে চরিত্রই বুঝি প্রধান, সন্দেহ নেই চরিত্রে গুরুত্ব অনেক কিন্তু চরিত্রের বাইরেও অনেক অনুষঙ্গ ও উপকরণ আছে-ঔপন্যাসিকের জীবনাভিজ্ঞতা, অবলোকন, আধ্যয়ন-অনুধাবন, উপস্থাপিত জীবনের সমস্যা ও সংকট এসবের অন্তঃবয়নের মধ্য দিয়ে জীবন বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্তের বিভিন্ন ইশারা আমরা পেয়ে যাই। শুধু তাই নয়, লেখকের মনীষা-দীপিত মননমুখ্য কল্পনাপ্রতিভা থাকাও জরুরি। বলাবাহুল্য, উত্তীর্ণ উপন্যাস বা গল্পের সারা শরীরে রচনাকারের ব্যক্তিত্ব খচিত কন্ঠস্বর মুদ্রিত থাকে, কিন্তু আমাদের কথাসাহিত্যে সেই প্রতিভার স্বাক্ষর কই?
ড. আহমেদ মাওলা, ডীন, বাংলা বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়