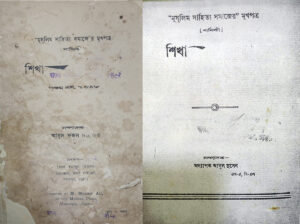শাহেদ কায়েস
একাত্তর বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অথচ রক্তস্নাত অধ্যায়। এটি একদিকে মুক্তির মহাকাব্য, অন্যদিকে অপমান, যন্ত্রণা ও লাঞ্ছনার ভয়াবহ ইতিহাস। নিরস্ত্র ও শান্তিপ্রিয় জাতি বাঙালির ওপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী চালিয়েছিল অকথ্য বর্বরতা যার নৃশংসতা হিটলারের নাৎসি বাহিনীকেও হার মানায়। গ্রাম-শহর জুড়ে হত্যাযজ্ঞ, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ ও ধ্বংসযজ্ঞের আগুনে জ্বলেছিল সমগ্র পূর্ববাংলা। কিন্তু ভয় বা ভেতো মনোবৃত্তির যে ছায়া দীর্ঘদিন বাঙালির কপালে আরোপিত ছিল, মুক্তিযুদ্ধ সেই অপবাদ মুছে দিয়েছে। সেদিন বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে হাতে তুলে নিয়েছিল অস্ত্র শুধু মাতৃভূমিকে রক্ষার জন্য নয়, বরং অমানবিকতার বিরুদ্ধে মানবিকতা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের পতাকা উড়ানোর দৃঢ় সংকল্পে। নিঃশেষ হওয়ার ভয়কে জয় করে এক নতুন জাতি তখন আত্মপ্রকাশ করেছিল স্বাধীনতার জন্য, অস্তিত্বের জন্য, মানুষের মর্যাদার জন্য।
একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ কেবল বাংলাদেশের জন্মের উৎসভূমিই নয়, এটি এক নতুন বাঙালি জাতিসত্তারও উন্মেষক্ষণ। সেই যুদ্ধে পুরোনো দাসত্বের পৃথিবী ভেঙে গিয়েছে, সামনে উন্মোচিত হয়েছে এক স্বাধীন, স্বপ্নময়, আত্মপরিচয়-সচেতন বিশ্ব। তাই স্বাভাবিকভাবেই মুক্তিযুদ্ধ আমাদের শিল্প-সাহিত্যের অন্তর্নিহিত স্পন্দনে অনিবার্য হয়ে উঠেছে। কবি ও কথাশিল্পী, নাট্যকার ও
চলচ্চিত্রনির্মাতা, চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর, সুরকার ও কণ্ঠশিল্পী সবাই তাঁদের সৃষ্টিশীলতার ভেতর দিয়ে সেই রক্তাক্ত গৌরবের দিনগুলিকে ধারণ করেছেন, ব্যথাকে রূপ দিয়েছেন শিল্পে, আর সংগ্রামকে রূপান্তরিত করেছেন সৌন্দর্যে। মুক্তিযুদ্ধ তাদের সৃষ্টির বিষয় নয়, প্রাণের উৎস হয়ে উঠেছে। তাই এই সৃষ্টিশীলতার ধারাই আমাদের জাতীয় ইতিহাসের ধারাবাহিক প্রতিচ্ছবি যেখানে সংগ্রাম ও স্বাধীনতার চেতনা মিশে আছে বাঙালির আত্মার গভীরে।
মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা, লাল-সবুজ পতাকা যে কোনো বাঙালির হৃদয়ে আলোড়ন তোলে গভীর মমতায়। ছন্দে ছন্দে রচিত গান, কবিতা ও কথাশিল্পে সেই স্পন্দনকে ধরে রেখেছেন কবি, কথাসাহিত্যিক, গীতিকার, সুরকার, কণ্ঠশিল্পী। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ছিল ১৯৭১ সালে বাঙালির হৃদয়ের খোরাক। স্মারক ডাকটিকিটের বর্ণিল অবয়বেও মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস-ঐতিহ্য প্রকাশিত হয়েছে অনবদ্য উচ্চতায়।
মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা, আর লাল-সবুজ পতাকা এই তিনটি শব্দই যেন এক অমোঘ জাদু, যা স্পর্শ করলেই জেগে ওঠে বাঙালির হৃদয়ের গভীরতম মমতা ও গর্ব। এই পতাকা শুধু রঙের সমাহার নয়, এটি এক জাতির আত্মত্যাগ, সংগ্রাম ও বিজয়ের প্রতীক। এর লাল অংশে রয়েছে রক্তের গল্প অগণিত শহীদের আত্মাহুতির আগুনে গড়া স্বাধীনতার সূর্য; আর সবুজ অংশে ফুটে আছে পুনর্জন্মের আশা, এক নতুন পৃথিবীর প্রতিশ্রুতি।
মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়টি ছিল এমন এক অধ্যায়, যখন গান, কবিতা, সুর, ও শব্দ সবই হয়ে উঠেছিল প্রতিরোধের অস্ত্র। কবি ও সাহিত্যিকরা শব্দে সৃষ্টি করেছেন আগুনের ভাষা, গীতিকার ও সুরকাররা সুরে বুনেছেন সাহসের মন্ত্র, আর কণ্ঠশিল্পীরা কণ্ঠে ছড়িয়ে দিয়েছেন মুক্তির আহ্বান। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ছিল তখন বাঙালির হৃদয়ের কেন্দ্রবিন্দু, যেন এক প্রেরণার বাতিঘর। এই বেতার কেন্দ্র থেকে ভেসে আসত গানের সুর, কবিতার আবৃত্তি, মুক্তিযোদ্ধাদের বার্তা যা দগ্ধ মনকে জাগিয়ে তুলত, হতাশ মানুষকে সাহস দিত, আর লড়াইরত জাতিকে একসূত্রে বাঁধত। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গানের প্রতিটি শব্দে ধ্বনিত হতো এক অদম্য প্রত্যয়, এক অনিবার্য বিজয়ের প্রতিজ্ঞা।
শুধু শব্দে নয়, দৃশ্যের ভাষাতেও মুক্তিযুদ্ধ খোদিত হয়েছে জাতির স্মৃতিতে। ডাক বিভাগের প্রকাশিত স্মারক ডাকটিকিটগুলো আজও বহন করে সেই ইতিহাসের রঙিন দলিল। সেখানে লাল-সবুজ পতাকা, মুক্তিযোদ্ধার বন্দুক, শরণার্থী মিছিল, কিংবা স্বাধীনতার আনন্দধ্বনি সবই প্রতিফলিত হয়েছে অনবদ্য শিল্পিত উচ্চতায়। প্রতিটি ডাকটিকিট যেন একটি ক্ষুদ্র চিত্রকাব্য, যেখানে একসঙ্গে কথা বলে বেদনা ও গর্ব, হারানো ও পাওয়া, মৃত্যু ও পুনর্জন্ম।
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস শুধু রণাঙ্গনের নয়, এটি সংস্কৃতি, কণ্ঠস্বর ও সৃষ্টিরও এক অবিস্মরণীয় ইতিহাস। ১৯৭১ সালের সেই নয় মাসে যখন সমগ্র দেশ দাউদাউ করে জ্বলছে আগুনে, তখন রক্তের পাশাপাশি প্রবাহিত হচ্ছিল এক শক্তিশালী শব্দধারা গান, নাটক ও চলচ্চিত্রের। এর কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, যা হয়ে উঠেছিল মুক্তিকামী জাতির হৃদস্পন্দন, মানসিক প্রতিরোধের অগ্নিশিখা এবং সাংস্কৃতিক সংগ্রামের প্রধান দুর্গ।
১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাত্রির পর পাকিস্তানি বাহিনী যখন সব সংবাদমাধ্যম ও রেডিও কেন্দ্র দখল করে নেয়, তখন জাতির কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে পড়ে। সেই স্তব্ধতার ভেতর থেকেই শুরু হয় মুক্তির রেডিওর নতুন ইতিহাস। প্রথমে চট্টগ্রামে, পরে কুষ্টিয়া, তারও পরে মেহেরপুর ও ত্রিপুরার আগরতলায় গড়ে ওঠে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, যার ডাকনাম ছিল ‘বাংলাদেশের অদৃশ্য রাজধানী’। এ কেন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল তিনটি মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণা ও দিকনির্দেশনা দেওয়া, দেশবাসীর মনোবল অটুট রাখা, এবং আন্তর্জাতিক পরিসরে বাঙালির সংগ্রামের খবর পৌঁছে দেওয়া। ‘স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র’ থেকে প্রতিদিন প্রচারিত হতো খবর, কবিতা, নাটক, ব্যঙ্গ-রচনা ও সবচেয়ে বড় কথা গান। এই গান শুধু বিনোদন ছিল না, এটি ছিল অস্ত্র, যা হতাশাকে সাহসে, কান্নাকে প্রতিবাদে রূপান্তরিত করত। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সবচেয়ে শক্তিশালী ও জনপ্রিয় দিক ছিল তার গান। কবি ও গীতিকাররা দিনরাত লিখে গেছেন নতুন গান যুদ্ধ, শোক, দেশপ্রেম ও প্রতিশোধের কথা। সুরকাররা সেই কথায় বুনেছেন অগ্নিস্বর, আর কণ্ঠশিল্পীরা ছড়িয়ে দিয়েছেন সর্বত্র।
গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের “শোন একটি মুজিবরের থেকে লাখ মুজিবরের কণ্ঠস্বর” ছিল মুক্তিযুদ্ধের প্রারম্ভিক দিনের আহ্বান, যেখানে বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠেছিলেন সংগ্রামের প্রতীক। আপেল মাহমুদের “মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি”, “তীরহারা এই ঢেউয়ের সাগর” কিংবা গোবিন্দ হালদারের “পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে রক্তলাল”ত্মএসব গান শুধু রেডিওতে নয়, মুক্তিযোদ্ধার হৃদয়ে বাজত প্রতিনিয়ত। এই গানগুলিতে যুদ্ধকে কেবল সংঘর্ষ হিসেবে নয়, এক মানসিক মুক্তির যাত্রা হিসেবে দেখা হয়েছে। গান হয়ে উঠেছিল স্মৃতির বীজ, সাহসের উৎস, ভবিষ্যতের বিশ্বাস। আর এই গানই পরে ১৯৯৫ সালে তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদের প্রামাণ্যচিত্র “মুক্তির গান”এর মূল উপাদান হিসেবে ইতিহাসে স্থান পায়।
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল নাটক ও শ্রুতিনাট্য প্রচার। যুদ্ধের সময় মঞ্চে নাটক করা ছিল প্রায় অসম্ভব; তাই রেডিওই হয়ে ওঠে বিকল্প মঞ্চ। এই শ্রুতিনাট্যগুলোয় যুদ্ধ, শরণার্থী জীবন, নারীর নির্যাতন, বিশ্বাসঘাতকতা ও মুক্তিযোদ্ধার সাহস সবই ফুটে উঠত জীবন্তভাবে।
সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়েছিল “চরমপত্র” একটি ব্যঙ্গাত্মক নাট্যধর্মী অনুষ্ঠান, যা পাকিস্তানি সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে ছিল রসিক অথচ তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ। প্রতিটি পর্বে “দাদা” চরিত্রের কণ্ঠে প্রচারিত হতো দুঃসংবাদের মধ্যে আশার আলো যেন কালো রাত্রিতে হাসির ঝলকানি। এই শ্রুতিনাট্য মানুষের মানসিক জড়তা ভেঙে দিয়েছিল। মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধের ফাঁকে ফাঁকে ট্রানজিস্টারে শ্রুতিনাট্য শুনে নতুন উদ্দীপনা পেতেন।
চলচ্চিত্র তখনও যুদ্ধের ভেতরে পূর্ণাঙ্গভাবে বিকশিত হয়নি, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধকে চলচ্চিত্রে ধারণ করার প্রচেষ্টা চলেছিল সমান্তরালভাবে। সবচেয়ে প্রভাবশালী ছিলেন জহির রায়হান যিনি “স্টপ জেনোসাইড” প্রামাণ্যচিত্রের মাধ্যমে পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার ভয়াবহতা আন্তর্জাতিক দৃষ্টিতে উন্মোচন করেন। তাঁর এই চলচ্চিত্র ছিল বাংলাদেশের পক্ষে এক বিশাল কূটনৈতিক অস্ত্র; ইউরোপ ও আমেরিকার সংবাদমাধ্যমে তা প্রচারিত হয়ে বিশ্ববিবেককে নাড়িয়ে দিয়েছিল। পরবর্তীতে চাষী নজরুল ইসলামের “ওরা ১১ জন”, আলমগীর কবিরের “ধীরে বহে মেঘনা”, সুভাষ দত্তের “অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী”, এবং তারেক মাসুদের “মুক্তির গান” সহ মুক্তিযুদ্ধের ওপর আরও অনেক চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে সবই সেই সাংস্কৃতিক ধারার উত্তরাধিকার বহন করে। বিশেষ করে ‘মুক্তির গান’ প্রমাণ করে যে, মুক্তিযুদ্ধ কেবল সামরিক ইতিহাস নয়, এটি এক সাংস্কৃতিক ও মানবিক পুনর্জন্মের কাহিনি।
গান, নাটক ও চলচ্চিত্র এই তিনটি মাধ্যম একত্রে যে ভূমিকা পালন করেছে, তা মূলত বাঙালি জাতির সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের এক জীবন্ত রূপ। যুদ্ধের সময় গান ছিল সাহসের জ্বালানি, নাটক ছিল চিন্তার উন্মোচন, আর চলচ্চিত্র ছিল ইতিহাসের দলিল। এই তিন মাধ্যম মানুষের মনের ভেতর স্বাধীনতার অর্থ নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে। যুদ্ধ কেবল বন্দুকের লড়াই নয় এটি ভাষার, সুরের, এবং দৃশ্যের লড়াইও। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে জন্ম নেয় এক নতুন ধরনের “জনমাধ্যম” যা সরকারের নয়, হয়ে ওঠে জনগণের কণ্ঠস্বর।
স্বাধীনতার পরও এই শিল্পধারা থেমে যায়নি। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গান, “চরমপত্র”-এর সংলাপ, জহির রায়হানের দৃশ্য সবই পরবর্তী প্রজন্মের সাহিত্য, চলচ্চিত্র ও নাটকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, মুক্তিযুদ্ধকালীন নাটক ও চলচ্চিত্র ছিল একাত্তরের নীরব অথচ প্রজ্জ্বলিত ফ্রন্টলাইন। এই মাধ্যমগুলো প্রমাণ করেছে যুদ্ধ শুধু গোলাবারুদের নয়, এটি কণ্ঠস্বর, কলম ও ক্যামেরারও। শিল্প তখন পরিণত হয়েছিল অস্ত্রে, সুর হয়ে উঠেছিল স্লোগানে, আর গল্প, উপন্যাস পরিণত হয়ে উঠেছিল ইতিহাসে। একাত্তরের গান, নাটক ও চলচ্চিত্র তাই কেবল অতীতের স্মৃতি নয় এগুলো বাংলাদেশের জাতীয় পরিচয়ের ভিত্তি, যেখানে শিল্প ও সংগ্রাম একই ছন্দে মিলেমিশে আছে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রতিটি সুর, প্রতিটি সংলাপ, প্রতিটি দৃশ্য আজও আমাদের মনে করিয়ে দেয় মুক্তিযুদ্ধ মানে কেবল স্বাধীনতা নয়, এটি এক অনন্ত মানবিকতা ও সাংস্কৃতিক জাগরণের প্রতিশ্রুতি।
মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলার গ্রামাঞ্চল কেবল যুদ্ধক্ষেত্র ছিল না তা ছিল প্রতিরোধ, প্রেরণা ও সৃজনশীলতারও উর্বর ভূমি। সেই গ্রামবাংলায়, যেখানে মাঠের ধান পুড়ে ছাই, নদীর জল লাল হয়ে উঠেছে রক্তে, আর ঘরহারা মানুষ অন্ধকারের ভেতর খুঁজে ফিরছে আলোর দিশা সেখানেই একদল অকৃত্রিম কবি, চারণকবি, জারি-সারি ও পল্লীগানের গায়ক তাদের নিজস্ব ভাষায় সৃষ্টি করেছিলেন স্বাধীনতার মহাকাব্য। এই কবিরা শহরের নামকরা সাহিত্যিক ছিলেন না, তাদের ছিল না কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, প্রকাশক বা মঞ্চ তবু তাঁদের কণ্ঠ ছিল মানুষের কণ্ঠ, তাঁদের ছন্দে ছিল গ্রামের মাটির স্পন্দন।
চারণকবিরা মুক্তিযুদ্ধের সময় রচনা করেছেন অসংখ্য গান ও কবিতা। গ্রামের প্রকৃতি যেমন সজীব ও বৈচিত্র্যময়, তেমনি এখানকার মানুষও আবেগপ্রবণ ও শিল্পমনস্ক। তাই কৃষক, জেলে, কামার, কুমার, বয়নশিল্পী, কিংবা নৌকার মাঝি সবার ভেতরেই যেন লুকিয়ে ছিল এক এক জন কবি। তারা তাদের জীবনের গল্প, দুঃখ, লড়াই, হারানো স্বপ্ন, আর মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে সুরে-ছন্দে বেঁধে তুলেছেন লোকগানের আকারে। এই গানগুলো ছিল কখনও শোকের, কখনও প্রতিবাদের, আবার কখনও মুক্তির আহ্বানে দীপ্ত।
একাত্তরে যখন পাকিস্তানি সেনারা গ্রাম দখল করে গণহত্যা চালাচ্ছিল, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই যখন আগুন ও রক্তের ভেতর দিয়ে বেঁচে থাকার সংগ্রাম করছিল, তখনই এই চারণকবিরা তাঁদের সৃষ্টিতে মানুষের মনে সাহস জাগিয়েছেন। তাঁদের গান অস্ত্রের চেয়ে কম শক্তিশালী হিল না। মুক্তিকামী মানুষ যখন ভয় আর হতাশায় কুঁকড়ে যাচ্ছিল, তখন গ্রামীণ কবিরা তাঁদের কণ্ঠে তুলেছিলেন যুদ্ধের ডাক “জয় বাংলা”, “মুক্তির গান”, “দেশ মাতৃকার জন্য প্রাণ দে রে ভাই”এইসব আহ্বান প্রতিধ্বনিত হয়েছিল মাঠে-ঘাটে, হাটে-বাজারে, মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে ও শরণার্থী শিবিরে।
চারণকবিরা কেবল গান রচনা করেননি, তাঁরা ছিলেন সেই সময়ের সংবাদদাতা, ইতিহাসলিপিকার এবং জনগণের প্রেরণাদাতা। তাঁদের অনেকেই যুদ্ধের প্রত্যক্ষ সাক্ষী নিজ চোখে দেখেছেন গণহত্যা, গ্রাম পোড়ানো, ধর্ষণ, শরণার্থীর মিছিল। এসব দেখেই তাঁরা লিখেছেন হৃদয়ের রক্তে ভেজা গান, যেখানে বেদনা ও প্রতিবাদ মিলেমিশে গেছে। তাঁরা শাসকগোষ্ঠীর অবিচার ও নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে কণ্ঠ তুলেছেন, সাধারণ মানুষকে সতর্ক ও ঐক্যবদ্ধ হতে আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁদের গান শোনা মানে ছিল সংগ্রামের আহ্বান শোনা, তাঁদের শব্দ-ছন্দে ছিল আগুন, কণ্ঠে ছিল স্বাধীনতার বিশ্বাস।
লোককবিদের বিশেষত্ব ছিল তাঁদের সহজ ভাষা ও অন্তরঙ্গ বর্ণনা। তাঁরা বক্তৃতার ভঙ্গিতে ইতিহাস বলেন না, বলেন হৃদয়ের স্বরে। যেমন কোনো মা তার সন্তানকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানোর আগে কাঁদতে কাঁদতে আশীর্বাদ করেন, তেমনি এই কবিতাগুলিতেও মিশে আছে মায়ের অশ্রু, প্রেমিকার প্রতীক্ষা, বন্ধুর বিদায় ও যোদ্ধার মৃত্যুবেদনা। একেকটি গান যেন একেকটি জীবন্ত দলিল যেখানে দেখা যায় গ্রামের অগ্নিদগ্ধ ঘর, নদীতে ভেসে থাকা লাশ, কিংবা শহীদের রক্তে ভেজা মাটি।
মুক্তিযুদ্ধ শেষে যখন দেশ স্বাধীন হল, তখনও এই চারণকবিরা থেমে থাকেননি। তাঁরা তাদের প্রত্যক্ষ করা ঘটনার স্মৃতি ধরে রাখতে, সেই দিনগুলোর ভয়াবহতা ও গৌরব নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে গেয়ে চলেছেন নতুন গান। তাঁদের কণ্ঠে ইতিহাস বেঁচে আছে, তাঁদের ছন্দে এখনও বাজে মুক্তির মন্ত্র। গ্রামের হাট-বাজারে, যাত্রাপালায়, মেলায় আজও সেই গান শোনা যায় যে গান একসময় ছিল যুদ্ধের প্রেরণা, এখন তা স্মৃতির রক্ষক, চেতনার ধারক।
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনায় এই চারণকবিরা এক অমূল্য সম্পদ। তাঁদের গান ও কবিতা থেকে আমরা পাই মানুষের ইতিহাস, প্রান্তিক জীবনের কণ্ঠস্বর, আর স্বাধীনতার সেই অপরিশ্রান্ত আকাঙ্ক্ষা, যা বইছে আমাদের লোকসংস্কৃতির ধমনিতে। তাঁরা প্রমাণ করেছেন সত্যিকার ইতিহাস শুধু বইয়ে লেখা হয় না, তা লেখা হয় মানুষের মুখে, গানে, অশ্রুতে, আর মাটির গন্ধে। তাঁরা আমাদের সাধারণ মানুষের কবি, অজ্ঞাত অথচ অমর। তাঁদের সৃষ্টিই দেখিয়ে দেয়, মুক্তিযুদ্ধ শুধু বন্দুকের লড়াই নয় এটি ছিল গান ও কবিতারও এক বিপুল সঙ্গীতযুদ্ধ, যেখানে প্রতিটি চারণকবি ছিলেন একেকজন অজানা সৈনিক, স্বাধীনতার চেতনার মশালবাহক।
এভাবেই মুক্তিযুদ্ধ আমাদের সাহিত্য, শিল্প, ও সংস্কৃতির অন্তঃস্থলে চিরস্থায়ী হয়ে আছে। গানের সুরে, কবিতার ছন্দে, গল্পের বর্ণনায়, উপন্যাসের দৃশ্যপটে, চিত্রকলার তুলিতে, নাটক ও চলচ্চিত্রের সংলাপে বারবার ফিরে আসে সেই একাত্তরের অগ্নিঝরা দিন, সেই লাল-সবুজ পতাকার ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকা বীরত্বগাথা। এইসব সৃষ্টিই আমাদের মনে করিয়ে দেয়, স্বাধীনতার গল্প কেবল অতীতের নয় এটি আজও জীবন্ত, প্রতিদিনের নিঃশ্বাসে, প্রতিটি প্রজন্মের হৃদয়ে নবীন হয়ে ওঠা এক চিরন্তন স্পন্দন।
শাহেদ কায়েস : কবি ও প্রাবন্ধিক