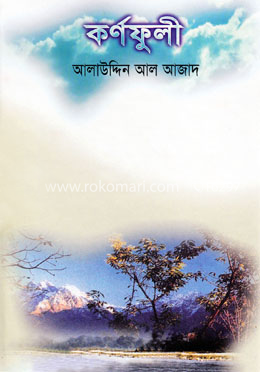আহমেদ মাওলা
উপন্যাসের নানা আঙ্গিক ও বিষয়-বৈচিত্র্যের কথা বিবেচনা করে সমালোচকগণ উপন্যাসকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করেন। সামাজিক উপন্যাস, রাজনৈতিক উপন্যাস, ঐতিহাসিক উপন্যাস, মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস, আত্মজীবনীমুলক উপন্যাস ইত্যাদি অভিধায় অভিসিক্ত হয়েছে বিশেষ বিশেষ ধরনের উপন্যাস। আঞ্চলিক উপন্যাস ও উপন্যাসের এমনি একটি শাখা। আঞ্চলিক উপন্যাসের শিল্পশৈলীর পৃথক ধ্রুব স্বাতন্ত্র্যে রয়েছে। ঘড়াবষ ড়ভ ঃযব ষড়াধষ পড়ষড়ৎ বা ঘড়াবষ ড়ভ ঃযব ংড়ষরষ নামে অভিহিত যে সব উপন্যাস, তা মূলত অঞ্চল বিশেষের রঙে রঞ্জিত। আঞ্চলিক উপন্যাসে নাম থেকেই স্পষ্ট হয়, অঞ্চলবিশেষের জীবনাশ্রয়ী এক বিশেষ শিল্পশৈলীর উপন্যাস। অঞ্চল বলতে কোনো নির্দিষ্ট ভূখ-ের জলবায়ু, মাটি, প্রাকৃতিক পরিবেশ, যা সেখানকার জনজীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে তাকেই বোঝানো হয় সেই ভূখ-ের অধিবাসীদের দৈহিক গঠন, মানসিক বিন্যাস, ভাষার ব্যবহার বিশেষ উচ্চারণ ভঙ্গি, সামাজিক নিয়মনীতি, বিশ্বাস সংস্কার, পোশাক-পরিচ্ছদ, জীবনযাত্রার অকৃত্রিম রূপ বোঝায়। ভাষা-সংলাপে স্থানীয় প্রবাদ-প্রবচন এমনকি উচ্চারণ ভঙ্গিকে এমনভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়, যাতে সেই অঞ্চলের পরিশেষ ধৃত পটভূমি থেকে চরিত্রগুলো কোনো ক্রমেই পৃথক করা যায় না। সেই অঞ্চলে বসবাসকারী শিষ্টজনের নয়, অপেক্ষাকৃত নি¤œশ্রেণি ও কৌম সমাজের জীবনের মধ্যেই আঞ্চলিকতার রূপ গাঢ়ভাবে পাওয়া যায়।
আমরা বলতে পারি, ‘কোনোঔপন্যাসিক যখন কোনো বিশেষ দেশাঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা, আচার, ব্যবহার, নিয়মনীতি, সমাজ-প্রেক্ষিত ও প্রাকৃতিক পরিবেশকে এমনভাবে তাঁর রচনায় রূপ দেন যাতে ঐ অঞ্চল যেন সেখানকার মানুষদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আত্মিক যোগে একটি স্বতন্ত্র চরিত্র হয়ে ওঠে এবং সেখানকার জনজীবনে তার সর্বাত্মক প্রভাবের মধ্য দিয়েও সর্বজনীন রসাবেদনে পৌঁছায় তখনই তাঁর রচনাকে ‘আঞ্চলিক উপন্যাস’ বলা যেতে পারে।’১ বাংলা উপন্যাসে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এধরণের রচনার ধারাটি সূচনা করেন।’২ উত্তরকালের তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), ‘গণদেবতা’ ‘হাঁসুলীবাঁকের উপকথা’; বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) ‘আরণ্যক’ ‘ইছামতি’; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬) ‘পদ্মানদীর মাঝি’; অদ্বৈত মল্লবর্মণের (১৯১৪-১৯৫১) ‘তিতাস একটি নদীর নাম’; সতীনাথ ভাদুড়ীর (১৯০৬-১৯৬৫), ‘ঢোড়াই চরিত মানস’ প্রভৃতি উপন্যাস আঞ্চলিক উপন্যাসের ধারাকে আরো সমৃদ্ধ করেছে।
উনিশ’শ সাতচল্লিশে ভারত বিভাগের পর বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকরা বাংলা উপন্যাসের এই প্রবহমান ঐতিহ্যকে অঙ্গীকার করে আঞ্চলিক উপন্যাস রচনায় সফল অবদান রাখেন। শহীদুল্লা কায়সারের (১৯২৫-১৯৭১) ‘সারেং বৌ’(১৯৬২); আলাউদ্দীন আল আজাদের (জন্ম ১৯৩২-২০০৯) ‘কর্ণফুলী’ (১৯৬২) সেলিনা হোসেনের (জন্ম ১৯৪৭) ‘পোকামাকড়ের ঘরবসতি’(১৯৮৬)আঞ্চলিক উপন্যাসের উজ্জ্বল উদাহরণ।
১.
কর্ণফুলী নদী ও তার তীরবর্তী বৈচিত্র্যময় জীবনপ্রবাহ, আঞ্চলিক পরিবেশধৃত শ্রমজীবী মানুষের আত্মদ্বন্দ্ব ও অস্তিত্বের স্বরূপ অঙ্কনের মানসে আলাউদ্দীন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯) রচনা করেন ‘কর্ণফুলী’ (১৯৬২) উপন্যাস। ঔপন্যাসিক লিখেছেন ‘চিত্রী যেমন বিভিন্ন রং দিয়ে একটি সৃষ্টি সম্পূর্ণ করেন, তেমনিভাবে আমি বিভিন্ন ভাষার রং ব্যবহার করেছি; ‘কর্ণফুলীর জীবনধারা, সবুজ প্রকৃতি,শ্যামল পাহাড় ও সাগর সঙ্গমে বয়ে চলা প্রবাহের মতোই এ ভাষা অবিভাজ্য। শিল্পসিদ্ধির জন্য এর অবলম্বন আমার কাছে অপরিহার্য রূপে গণ্য হয়েছে।’৩ ঔপন্যাসিক আঞ্চলিক লোকজীবন ও ভাষার অঙ্গীকারের কথা যতই উচ্চারণ করুন না কেন, ‘কর্ণফুলী’ সর্বোতভাবে আঞ্চলিক উপন্যাস নয়। কারণ, আঞ্চলিক উপন্যাসের যে সব বৈশিষ্ট্য -‘প্রথমত, কোন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের নিবিড় এবং অখ- পরিচয় দান, দ্বিতীয়ত, ভাষা-সংলাপে,স্থানীয় প্রবাদ প্রবচন এমনকি উচ্চারণ ভঙ্গিতেও সাধ্যমতো আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলা’৪ ইত্যাদি।‘কর্ণফুলী’ উপন্যাসে পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যায় না। আঞ্চলিক বৃত্তাবদ্ধ জীবনকাঠামো নগরায়ণ ও যন্ত্রায়নের ফলে যে রূপান্তর ঘটে, তারই দৃষ্টিগ্রাহ্য বাস্তবতা শিল্পায়িত হয়েছে এ উপন্যাসে। অন্তঃপ্রবাহে রোমান্টিকতা থাকা সত্ত্বেও ,বিশেষ অঞ্চলের জীবনপ্রবাহের শব্দরূপ হিসেবেই ‘কর্ণফুলী’ উপন্যাসের বিশেষত্ব।
৩.
কাহিনীগঠনে বিশেষ ভৌগোলিক আয়তনের বস্তুসমগ্রতা থাকলেও আর্থ সামাজিক কাঠামোর অন্তর্গত নৃতাত্ত্বিক ঐতিহ্যম-িত মানবসম্প্রদায়ের সুসংহত রূপবন্ধনে ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিকোণ পরিশ্রুত নয়। ঔপন্যাসিকের সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতাই এর জন্য দায়ী। জীবনানুভাবে রোমান্টিকতার কারণে চরিত্রের ভাবনা-কল্পনা আচার উচ্চারণে স্থূলতা এসেছে, যা দখড়পধষ পড়ষড়ঁৎ ধহফ যধনরঃধঃরড়হ কে পূর্ণাঙ্গ শিল্পরূপক দিতে সর্বাংশে সফল হয়। উপন্যাসের শুরুতেই আঞ্চলিক জীবন প্যাট্যার্নের স্বরূপ স্পষ্ট হয় :
‘সুড়ঙ্গের মতো অন্ধকার গলি, তার ভিতরে বাঁশের চোটেপা কামার শালা। বাঁহাতে শেকল ধরে টাকা হাপরের গনগনে আগুন মিস্ত্রির পেশীবহুল কালো দেহটাকে মোটা রেখায় উৎকীর্ণ করেছে এবং সেই রক্তিম আভায় রঙিন হয়ে থাকা তার মুখ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরছে ঘাম।’৫
এই কামারশালায় ঠিকাদার রমজানের সঙ্গে পটেকমার ইসমাইলের কাজের কথা হয় এবং তার জন্য অগ্রিম নেয় বেশটাকা। বাড়িতে এসে মা মনুবিবিকে সেই দশটাকা হাতে দেয় এবং তার কেরামতের মেয়ে জুলির বিয়ের কথা শুনে মনে মনে রোমান্স অনুভব করে। জুলিকে তার ভালো লাগে, তবে বিয়ে করে দায়িত্ব নেয়ার কথা কখনো ভাবেনি। তবে একবার সে জুলিকে একটি সোনার আংটি দিয়েছে। মা মনুবিবির সঙ্গে ইসমাইলের যখন কথা হয় তখন আড়াল থেকে জুলি তা শুনে,
হাতের আংটিটা খুলে আচমকা সে ইসমাইলের কোলের ওপর ফেলে পালিয়ে যায়। যদিও রমজানের সঙ্গে কাসালং যাওয়ার পূর্বে সে একবার জুলিদের বাড়ি যায়, মনের গোপন ইচ্ছা, যদি জুলির সঙ্গে একটু কথা হয়। জুলির বাবা কুলি কেরামতের সঙ্গে কথা বলে, জুলি কাছে আসে না।
রমজানের সঙ্গে ইসমাইল কাসালং বাঁকটাতে যায়। রমজান কর্ণফুলী পেপার মিলের বাঁশের ঠিকাদার। রমজানের কাজে কাসালং গিয়ে ইসমাইল পরিচিত হয় লালচাচার সঙ্গে। স্বভাবে লালচাচা একটু ক্ষেপাটে, বেশি আসক্তি দেশি মদের দিকে। দ্বিতীয় রাতেই ইসমাইল বুঝতে পারে টাকা ও মদ দিয়ে রমজান লালচাচার কাছে থেকে কিনতে চায় তার মেয়ে রাঙামিলাকে। দুপুরে কলসি জল দিতে এলে রাঙামিলার সঙ্গে পরিচয় হয় ইসমাইলের। বিকেলে ঝর্নায় জল আনতে গেলে ইসমাইল জুলির ফেরত দেয়া আংটি দেয় রাঙামিলার কলসিতে। অবশ্য কয়েকদিন পর লালচাচার বাড়িতে গিয়ে সে রাঙামিলার জন্য একটা শাড়িও দিয়ে আসে। কিন্তু রাঙামিলাকে ভালোবাসে চাকমা যুবক নীলমনি। রাঙামিলাও নীলমনির প্রেমের যোগ্য স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত। তারা রাতের আঁধারে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করে। ইসমাইল গাছের আড়ালে থেকে তাদের পালিয়ে যাওয়ার কথা শুনে ফেলে। জিঘাংসায় ইসমাইলের চোখ জ্বলে ওঠে। নির্ধারিত রাতে রাঙামিলা নীলমনির হাত ধরে পথে নামে। ইসমাইলও তাদের অনুসরণ করে। কিন্তু ইসমাইল জানতো রমজান, ইতুগু-া, হাবুগু-া তাকেও অনুসরণ করছে। পথের ক্লান্তিতে রাঙামিলা নদীর তীরে এসে বিশ্রাম নেয় নীলমনির কোলে মাথা রেখে। হঠাৎ রাঙামিলার চোখে পড়ে সমাইল। নীলমনি উঠতে যাচ্ছিল, এমন সময় ইসমাইলের দুপাশ থেকে ইতুগু-া ও হাবুগু-া এসে দাঁড়ায়। সুযোগ বুঝে তাদেরকে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে নীলমনি ইসমাইলের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। কিন্তু নীলমনি পরাস্ত হয়। সে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললে তার জন্য ইসমাইলের মনে সহানুভূতি জাগে। নীলমনিকে কাঁধে নিয়ে রাঙামিলাসহ ইসমাইল এগিয়ে চলে। বাড়ি এসে ইসমাইল শুনতে পায় জুলির বিয়ের কথা। সে রাতেই জুলিকে ডেকে এসে ঘরের লাইট নিভিয়ে দেয়। পরে অবশ্য জুলিকে সে বিয়ে করে। জুলির ঘরে তার সন্তান হয়। এদিকে কুলির কাজ যেমন তার ভালো লাগেনা, তেমনি সংসার চালানো তার জন্য কষ্টকর হয়ে ওঠে। একসময় দুজন ভদ্রলোকের সঙ্গে তার পরিচয় হয়, তাদের সাহায্যে ইসমাইল ‘নলি’ হয়, তবে শর্ত থাকে যে, জাহাজে সে তাদের হয়ে কাজ করবে। জাহাজে যাওয়ার পূর্বে ইসমাইল জুলিকে আদর করে, সান্ত¡না দেয়, জুলির চোখের জল কর্ণফুলীর নোনাজলে মিশে যেতে থাকে। জাহাজ দৃষ্টির বাইরে চলে গেলে জুলি ফিরে আসে বাস স্ট্যান্ডের দিকে। উপন্যাসটি শেষ হয় এভাবে।
‘আসমান ওপরে থাক, দরিয়াকে ভয় করা যায়না? আস্তে আস্তে হেঁটে বাসস্ট্যান্ডের দিকে যেতে এ কথাটিই মনে জেগে থাকে ধ্রুবতারার মতো। তার কানে বাজে বহুবার শোনা গানের কলি, রঙ্গম রঙ্গিলা সনে মর্জি রইল মন, এ মত দেওয়ানারে হইয়া ও লি কতজন, রঙ্গম রঙ্গিলারে।’ ৬
এই পরিসমাপ্তিতে বোঝা যায়, কাহিনীগঠনে ও চরিত্র বিন্যাসে আলাউদ্দিন আল আজাদ সচেতন ছিলেন না। কাহিনী কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য পথে এগিয়ে যায়নি। অর্থাৎ ঔপন্যাসিক শুরু থেকে পরিণতি নিয়ে ভাবেননি, তাই ঘটনার বিন্যাস এলোমেলো। উপন্যাসে মূল চরিত্র ইসমাইল, তার পরিচয় প্রথমে পকেটমার, গু-া, অবশেষে যে এক বিশেষ গোষ্ঠীর কর্মি হয়ে জাহাজে যাত্রা করে। আঞ্চলিক উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে ইসমাইলের কোনো পরিচয় ফুটে ওঠে না। এমনকি সে কোনো পেশার বা গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে না। অথচ ঔপন্যাসিক তাকে শ্রমজীবী মানুষের প্রেক্ষাপটে চিত্রিত করেছেন। এছাড়াও ইসমাইল প্রথমে জুলির প্রতি আকৃষ্ট হলেও তার এ আকর্ষণ যেন সাময়িক, কাসালং বাঁশ কাটতে গিয়ে আবার রাঙামিলার প্রতিও আকর্ষণ অনুভব করে। তাকে জুলির ফিরিয়ে দেয়া আংটি দেয়, এমনকি তার বাড়িতে গিয়ে শাড়িও দিয়ে আসে। রাঙামিলা তার প্রেমিক চাকমা যুবক নীলমনির হাত ধরে বেরিয়ে যাওয়ার রাতে ইসমাইল হাতে ডেগার নিয়ে তাদের অনুসরণ করে অন্যদিকে তাকেও অনুসরণ করে রমজান, ইতুগ-া, হাবুগু-া। দ্বন্দ্বযুদ্ধে নীলমনি সংজ্ঞা হারালে সে অবশ্য তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয় এবং তাকে কাঁধে করে রাঙামিলাসহ শহরে আসে। এখানে ইসমাইলের চরিত্রে মানবিকতার স্পর্শ দেখা যায়। কিন্তু বাড়ি ফিরে যখন শুনতে পায় জুলির বিয়ে হয়ে গেছে তখন আবার জিঘাংসা জেগে ওঠে। জুলিকে ডেকে এসে ঘরের লাইট নিভিয়ে নিয়ে তার পাশবিকতা চরিতার্থ করে। অর্থাৎ নারীর প্রতি তার আকর্ষণ যতটুকু তার চেয়ে বেশি শারীরিক। যদি সেই জুলিকেই শেষ পর্যন্ত বিয়ে করে কিন্তু তাকে প্রেমিক পুরুষ বলে মনে হয়না। ইসমাইলের চরিত্র চিত্রণে আলাউদ্দীন আল আজাদের এই
অসর্তকতা বিশৃঙ্খলতা ‘কর্ণফুলী’ উপন্যাসের গঠনবিন্যাসকে দুর্বল করে ফেলেছে। উপন্যাসের অন্য চরিত্রগুলোর মধ্যে রমজান কর্ণফুলী পেপার মিলের বাঁশের ঠিকাদার। শ্রেণি চরিত্র অনুযায়ী রমজাদ অর্থলোলুপ, নারীলোলুপ লম্পট। রাঙামিলাকে পাওয়ার জন্য সে তার পিতা লালচাকে মদ খাওয়ার টাকা দিয়ে এবং শেষ পর্যন্ত ইতুগু-া ও হাবুগু-া কে নিয়ে নিজেই রাঙামিলা ও নীলমনিকে অনুসরণ করে। অর্থাৎ সে যথার্থই তার শ্রেণিচরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে। রাঙামিলা ও জুলি দুজন ইসমাইলের জীবনের স্বপ্ন ্-আকাক্সক্ষার কারণ ছিলো। কিন্তু জুলির অভিমান যেমন ইসমাইলকে রাঙামিলার প্রতি আগ্রহী করেছে তেমনি আবার বিপথগামী করেছে। জুলি এবং রাঙামিলা এই দুই নারী চরিত্র কর্ণফুলী উপন্যাসের স্বপ্নময় পরিবেশ তৈরি করেছে। তবে তাদের চরিত্র প্রেমের জন্য ত্যাগ কিংবা সংগ্রাম কোনো কিছুই লক্ষ করা যায় না। রাঙামিলা নীলমনিকে ভালোবেসে পথে নামে সত্য কিন্তু তাদের পরিনাম ঔপন্যাসিকের যথার্থ পরিচর্যা থেকে বঞ্চিত। ঔপন্যাসিকের মূল আকর্ষণ ছিলো আঞ্চলিক জীবনের পরিবর্তনের প্রতি। ইসমাইলের দৃষ্টিতে সেই পরিবর্তনের রূপ ধরা পড়ে এভাবে :
ক. ‘মিলের বাঁশ কাটার মেশিনটা আজব জিনিষ, যেন রূপকাহিনির রাক্ষস, প্রচ- শব্দে কাজ করে চলেছে, বড় বড় বোন্দাগুলি নিমিষেই মিশমার। কাপ্তাইয়ের বিজলীঘর, ছোড়, দরওয়াজা, কলের এত শক্তি। এদের কাছে মানুষের মেহেনত তো কিছু নয় ? পাহাড়কে বদলাচ্ছে, মাটিকে বদলাচ্ছে, যাদুমন্ত্রের মতো।’৭
খ. ‘বছর খানেকের মধ্যে গ্রাম ছেড়ে দিয়ে এখানকার সকলকেই চলে যেতে হবে। কাপ্তাই-এর বিজলী-কারখানা চালু ভেসে যাবে এই এলাকাও।’৮
অর্থাৎ বহির্বাস্তবতার আঘাতে, যন্ত্রায়ন ও নগরায়নের ফলে আঞ্চলিক জীবনকাঠামোর যে রূপান্তর সাধিত হচ্ছে, তার সঙ্গে স্থানীয় অধিবাসীদের জীবনপ্যাট্যার্নের পরিবর্তন হচ্ছে। উপন্যাসের পরিসমাপ্তিতে তাই দেখা যায় কেন্দ্রীয় চরিত্র ‘নলি’ বানিয়ে জাহাজে পাড়ি জমায়। উপন্যাস নির্মিতির সুদক্ষ স্বাক্ষর থাকা সত্ত্বেও আলাউদ্দিন আল আজাদের ‘কর্ণফুলী’ সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতার উপন্যাস বলে অনুমিত হয়। শ্রমজীবী মানুষের প্রতি মমত্ববোধ থাকার কারণে আলাউদ্দিন আল আজাদ চরিত্র নির্বাচনে নি¤œশ্রেণীর -কুলি, মজুর, ঠিকাদার, চরিত্রকে প্রাধান্য দিলেও ‘কর্ণফুলী’ শ্রেণিচেতনার উপন্যাস নয়। ‘কর্ণফুলী’ উপন্যাসের আন্তঃবিন্যাস রোমান্স আক্রান্ত, আঞ্চলিক গীতলতায় পরিপূর্ণ।
৪.
‘কর্ণফুলী’ উপন্যাসের ভাষা ব্যবহারে আলাউদ্দিন আল আজাদ চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গান, প্রবাদ-প্রবচন প্রয়োগ করে স্থানীয় জীবনধারাকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। সবক্ষেত্রে তিনি সফল হয়েছেন, এমন বলা যায় না। কারণ, আঞ্চলিক শব্দের অসর্তক প্রয়োগ, ও আঞ্চলিক উচ্চারণভঙ্গির ভুল বানান দৃষ্টি এড়ায় না।
‘ইসমাইল একটি স্থির হয়ে চাঁদে আলোতে ওর পদ্মের মতো মুখ, তারপর হাত ছাড়িয়ে রেখে আগলে বুকের কাছে ধীরে বলল: ‘ন ডরইও। চল জলদি। দোহরা পথ দিষওন পড়িব।’ (কর্ণফুলী / পৃ. ৩৬)
এখানে সংলাপের মধ্যে ‘চল জলদি’ -এর চল’ স্থানীয় উচ্চারণ ‘চলঅ’ এবং ‘দিষওন’ শব্দটি আঞ্চলিক উচ্চারণে হবে ‘দিশ্ হঅন’ অর্থাৎ সঠিকভাবে পাওয়া। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গানের ব্যবহার :
ক. রইস্যা বন্দু ছাড়ি গেলরে
শাদা দিলে দাগ লাগাই।
খ. নিডির তলি মারবহিব
পশারি দুগান লবহিব
লাইবে এবারৎ ইলে
বাজি পারে নায় কোনদিন।
আঞ্চরিক প্রবাদ-প্রবচন :
যদি আছে দুই পাও, যেথা ইচ্ছা সেথা যাও
যদি হবে চার পাও, এই ব্যাটা কোথা যাও
যদি হও ছয় পাও, আব্বাজান মিশ্রি দাও।’ ’৯
আলাউদ্দিন আল আজাদ ‘কর্ণফুলী’ উপন্যাসের ‘লেখকের কথা’য় যদিও বলেছেন – ‘চিত্রী যেমন বিভিন্ন রং দিয়ে একটি সৃষ্টি সম্পূর্ণ করেন, তেমনিভাবে আমি বিভিন্ন ভাষার রং ব্যবহার করেছি। কর্ণফুলীর জীবনধারা, সবুজ প্রকৃতি, শ্যামল পাহাড় ও সাগর সঙ্গমে বয়ে চলা প্রবাহের মতোই এ ভাষা অবিভাজ্য।’ কিন্তু‘ আমাদের বিবেচনায় এ ‘অবিভাজ্য’ ভাষা তিনি অকৃত্রিমভাবে প্রয়োগ করতে পারেননি। বিচ্ছিন্নভাবে প্রয়োগের ফলে ভাষার আঞ্চলিক রঙ পরিস্ফূট হয়নি। আঞ্চলিক জীবনধারার অকৃত্রিম ছবি আঁকতে গেলে অবশ্যই আঞ্চলিক অবিভাজ্য ভাষার অকৃত্রিম প্রয়োগ করতে হবে। তবু নদী কর্ণফুলীর তীরবর্তী জীবনধারা যে ছবি আলাউদ্দিন আল আজাদ আমাদের সাহিত্যে উপহার দিয়েছেন তা সর্বাংশে আঞ্চলিক সার্থকতা পরিপূর্ণ না হলেও বাংলাদেশের উপন্যাসে সুনির্দিষ্ট ব্যতিক্রম।
তথ্যনির্দেশ ও টীকা
১. অলোক রায় (সম্পাদিত), সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য, সাহিত্যলোক, দ্বি. স. ১৯৯৩, কলকাতা,পৃ. ৩
২.গোপিকানাথ রায় চৌধুরী, দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যকালীন কথাসাহিত্য,১৯৮৬,কলকাতা,দে’জ পাবলিশিং, পৃ. ২৮৩
৩.রফিকউল্লাহ খান : বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ , পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৬
৪.আলাউদ্দিন আল আজাদ, কর্ণফুলী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৪, ঢাকা, মুক্তধারা, দ্রষ্ট্রব্য-‘লেখকের কথা’ ৫.অরূপ কুমার ভট্টাচার্য, আঞ্চলিকতা :বাঙলা উপন্যাস, ১৯৮৭, কলকাতা, পুস্তক বিপনী, পৃ. ৬
৬.কর্ণফুলী, পূর্বোক্ত, পৃ.৯
৭.কর্ণফুলী, পূর্বোক্ত, পৃ.১৩২
৮.কর্ণফুলী, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৩
৯.কর্ণফুলী, পূর্বোক্ত, পৃ.৪২
ড. আহমেদ মাওলা, ডীন, বাংলা বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়