মহীবুল আজিজ
বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এক অনন্য সাধক উইলিয়াম রাদিচে’র নাম তাঁর বাঙালিত্বের সাধনার জন্য সমগ্র পৃথিবীতে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। তাঁর অনূদিত রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প সমালোচকদের বিচারে এযাবৎ ভাষান্তরিত হওয়া সবগুলো টেক্সটের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্য’র সম্পূর্ণ অনুবাদ করেছেন দুই ইংরেজিভাষী- মার্কিন ক্লিনটন বুথ সিলি এবং ইংরেজ রাদিচে। তাঁর অনুবাদটাই শ্রেয়তর বলে স্বীকৃত। রবীন্দ্রনাথের নাটক, ক্ষুদ্র কবিতা, কবিতার আশ্রয়ে নির্মিত অপেরা সবই তাঁর ভালোবাসা ও অনিঃশেষ মুগ্ধতার প্রকাশ। বাঙালি জাতিসত্তার এমন একজন সাংস্কৃতিক দূতের প্রয়াণ বড়ো বেদনার। বিশেষ করে সেই মহান মানুষটির সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ের ইতিহাস সেই বেদনাকে করে গাঢ়তর। উইলিয়াম রাদিচে’র (১৯৫১-২০২৪) সঙ্গে পরিচয় ১৯৯০ সালের দিকে। চট্টগ্রাম বিশ^বিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. মনিরুজ্জামানের আমন্ত্রণে তিনি এসেছিলেন ইংল্যান্ড থেকে।
ক্যাম্পাসে মনিরুজ্জামান স্যারের বাসাতেই ছিলেন তিনি। সেখানে থেকেই বিশ^বিদ্যালয় লাইব্রেরি বাংলা বিভাগ এবং শহরের নানা জায়গায় অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন। আমার মতন একজন তরুণ প্রভাষককেও তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন, এটা ভেবে এতকাল পরে এসে আজও তাঁর এই প্রয়াণের পরে মনের গহিনে বেদনা বোধ করি। বাংলাদেশ বাংলা ভাষা-সাহিত্যই যে কেবল এক পরম সুহৃদকে হারালো তা-ই নয়, বাংলা ভাষা-সাহিত্য ও পাশ্চাত্যজগতের মধ্যকার এক মজবুত সেতুবন্ধ মিলিয়ে গেল তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে।
প্রথমবারের সেই অবস্থানে তিনি বিভাগে বক্তৃতা দেন রবীন্দ্রনাথের ক্ষুদ্রাকৃতি কবিতা বিষয়ে, বিশেষ করে ‘কণিকা’ কাব্যগ্রন্থের কবিতাবলি সম্পর্কে। তাঁর পরিচিতি উপস্থাপন করেন আমাদের প্রায় সকলের শিক্ষক ভাষাবিজ্ঞানী ড. মনিরুজ্জামান। জানতে পারি রাদিচে মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য বিষয়ক গবেষকই শুধু নন, তাঁদের সাহিত্যের এক অসাধারণ অনুবাদকও। পরেও আসেন তিনি আমাদের বিভাগে, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বক্তৃতা দেন, যেটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ মিলনায়তনে। বিভাগে এলে অনেক সময় তিনি দুপুরের খাবার খেতেন আমাদের শিক্ষক লাউঞ্জে। এক টেবিলে সকলের সঙ্গে খাদ্যগ্রহণের সামাজিকতায় তাঁকে কাঁটাচামচের ব্যবহার বর্জন করতে দেখি। তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের পরিসর কালক্রমে বাড়ে এবং ১৯৯১ সালের নভেম্বর থেকে পরবর্তী বছর পাঁচেক আমার ইংল্যান্ডে অবস্থানের সুযোগে সেটি পারস্পরিক জানাশোনার দিকে এগোয়। আমার পক্ষে এই নিবেদিতপ্রাণ মানুষ ও তাঁর কর্ম তাঁর অনন্য-সমৃদ্ধ পারিবারিক ঐতিহ্য-ইতিহাস সম্পর্কে জানার অবকাশ সৃষ্টি হয়।
ইটালো দ্য লিল রাদিচে এবং বেটি রাদিচের পাঁচ সন্তানের মধ্যে উইলিয়াম চতুর্থ। ভাইবোনের মধ্যে তৃতীয় থেরেসার মৃত্যু হয় শৈশবে। দ্বিতীয় ক্যাথারিন মারা যান তাঁর টিনইয়ার্সের শেষ দিকে। সবার বড় থমাস ছিলেন প্রভাবশালী সরকারি কর্মকর্তা। সবার ছোট জন সম্পর্কে জানতে পারি নি। রাদিচের জ্ঞান-ঔদার্য-সূক্ষ্মতার শেকড়ের সন্ধান করতে গেলে যেতে হবে তাঁর জন্মদাত্রী মা বেটি রাদিচের (১৯১২-১৯৮৫) নিকটে। এই মহিয়সী মহিলার ঋণ স্বয়ং রাদিচে স্বীকার করেন অকুণ্ঠভাবে। ইংল্যান্ডে তাঁদের প্রাথমিক বসবাস ইয়র্কশায়ার অঞ্চলে যদিও তাঁদের বংশের আদি পুরুষেরা ছিলেন ইতালিয়। ধ্রুপদী ভাষা-সাহিত্যে উচ্চতর ডিগ্রিধারী বেটি ছিলেন ল্যাটিন ভাষায় পারদর্শী এবং ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে ল্যাটিন ভাষা-সাহিত্যের একজন নামকরা অনুবাদক। রাদিচের দেওয়া বিভিন্ন সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, অনুবাদের শৈল্পিক পারদর্শিতা এবং অনুবাদে মূলের সূক্ষ্মতা কিভাবে ফুটিয়ে তুলতে হয় সেটা তিনি অল্প বয়সেই মায়ের কাছ থেকে শিখেছিলেন। অক্সফোর্ডে শিক্ষালাভকারী বেটির পারঙ্গমতা ছিল ইংরেজি, ল্যাটিন, ধ্রুপদী সাহিত্য এবং দর্শনশাস্ত্রে। বিখ্যাত ‘পেঙ্গুইন ক্ল্যাসিক্স’-এর যুগ্ম সম্পাদক, সম্পাদক এবং ‘ক্ল্যাসিক্স এসোসিয়েশন’-এর সহ-সভাপতি বেটি’র অসাধারণ সব রচনা আজও স্মরণীয়। রোমক ঐতিহাসিক প্লিনি’র চিঠিপত্র, টেরেন্স এবং ইরাসমুসের রচনা এবং ‘হুজ হু ইন দ্য এনশিয়েন্ট ওয়র্ল্ড’ এইসব মূল্যবান রচনা’র তিনি অনুবাদক। তাঁর মৃত্যুর দু’বছর পর পুত্র উইলিয়াম এবং বারবারা রেনল্ডস্-এর সম্পাদনায় পেঙ্গুইন থেকে প্রকাশিত ‘ফেস্টস্খ্রিফ্ট’ (‘এসেজ ইন অনার অব বেটি রাদিচে’) ‘দ্য ট্রান্সলের্টস্ আর্ট’ শীর্ষক গ্রন্থটি বলা যায় বেটির অমরত্বের পরিধি আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। অনন্য এ-গ্রন্থের প্রবন্ধসমূহে মুদ্রিত সুসম্পাদনার ছাপ।
লন্ডনের ওয়েস্টমিনিস্টার স্কুল এবং অক্সফোর্ডের মডলেন কলেজের শিক্ষার্থী উইলিয়াম রাদিচের সাহিত্যপ্রতিভার প্রকৃত স্ফূরণ ঘটে তাঁর ইংরেজি সাহিত্যে অধ্যয়নের সময়টাতেই। ১৯৭০ সালে কবিতা রচনার স্বীকৃতি হিসেবে অর্জন করেন নিউডিগেট পুরস্কার। পেশাগত জীবনে সাইকিয়াট্রিক নার্স এবং স্কুলশিক্ষকতার চাকুরি করেন কয়েক বছর। অনেকের ধারণা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা রাদিচেকে বাংলাদেশ বাংলা ভাষা-সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে আকৃষ্ট করে এবং তিনি অক্সফোর্ডে বাংলা সাহিত্য নিয়ে উচ্চতর পর্যায়ের শিক্ষা ও গবেষণায় উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। অক্সফোর্ড থেকে তিনি ডি.ফিল ডিগ্রি নেন মাইকেল মধুসূদন দত্তের সাহিত্য বিষয়ে কিন্তু বাংলা সাহিত্যের বিচিত্র বিষয়ে বিশেষ করে রবীন্দ্র সাহিত্যের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয় তাঁর সামনে এবং তিনি সেই থেকে রবীন্দ্রনিমগ্ন এক বিরামহীন পথিক যে-পথে যতি পড়ে তাঁর পরলোকগমনের মধ্য দিয়ে। এখানে স্মরণযোগ্য ভারতীয় উপমহাদেশে এবং বাংলাদেশে তাঁর রবীন্দ্রচর্চা ও অনুবাদসত্তার পরিচিতি যতটা ব্যাপক তাঁর মৌলিক বা সৃজনশীল সাহিত্যচর্চার প্রচার ততটা নয়। ১৯৭৪ থেকে ২০০৪ সালের ব্যবধানে তাঁর যে-ছয়টি মৌলিক কাব্যগ্রন্থ Eight Sections, Strivings, Louring Skies, The Retreat, Gifts Ges This Theatre Royal প্রকাশিত হয় তাতেই তিনি ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসেও নির্ধারিত আসন পেয়ে যান। এছাড়া ১০১টি সনেটের অবলম্বনে রচিত ২০০৫ সালে প্রকাশিত তাঁর Green, Red, Gold উপন্যাসটি যথেষ্ট প্রশংসিত হয় সাহিত্য-সমালোচকমহলে। সমালোচক এ. এন. উইলসন ইংল্যান্ডের ‘ডেইলি টেলিগ্রাফ’-এ এটির প্রশংসাসূচক পর্যালোচনা করেছিলেন। ১৯৮৬ সালে বিক্রম শেঠ রচিত (৫০৬টি সনেটের সহযোগে) ‘দ্য গোল্ডেন গেট’ পরে প্রকাশিত হলে রাদিচেই পেতেন সনেট-উপন্যাস রচনায় পথিকৃতের স্বীকৃতি।
আমার দৃষ্টিতে উইলিয়াম রাদিচে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবদান রাখা আরেক মহান ব্যক্তিত্ব তাঁরই স্বদেশী জেমস ড্রমন্ড এন্ডার্সনের (১৮৫২-১৯২০) যথার্থ উত্তরসূরী। আবার, উভয়েরই রয়েছে রবীন্দ্রনাথ এবং বাংলা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও বাঙালিসংলগ্নতা। এন্ডার্সনের মৃত্যুর অর্ধ শতাব্দীকাল পরে তাঁরই জন্মভূমিতে সূচনা ঘটে এককালের ব্রিটিশ উপনিবেশ বাংলার জীবন ও সমাজের ক্ষেত্রে নিবেদিতপ্রাণ আরেক মহান ব্যক্তিত্বের সৃজন-মননশীল কর্মের। ১৯৯০ সালে রাদিচে লন্ডনস্থ SOAS (সেন্টার অব সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ)-এ বাংলা বিষয়ে লেকচারার হিসেবে যোগ দেন। তাঁরই শিক্ষক বিশিষ্ট গবেষক-প্রাবন্ধিক তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে পদটি শূন্য হয়ে গিয়েছিল। ১৯৯১-এর নভেম্বরে আমাকে ইংল্যান্ডে যেতে হয় এবং রাদিচের চট্টগ্রামে অবস্থানকালে তাঁর সঙ্গে খানিকটা যোগাযোগের সূত্রে আমি তাঁকে টেলিফোন করি কেম্ব্রিজ থেকে। ফোনে তাঁকে প্রসন্ন ও উচ্ছ্বসিত মনে হলে আমি এক চমৎকার সকালে তাঁর সঙ্গে দেখা করি ‘সোয়াস’-এ তাঁর কর্মস্থলে। সেখানে এবং ক্যাফেটেরিয়ায় চলে আমাদের আলাপ। তাঁর অতি ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি যথেষ্ট মনোযোগে আমাকে শোনেন। সেখানে পরিচয় ঘটে তাঁর অধীনে পিএইচডি কোর্সের শিক্ষার্থী এক নরওয়েজিয় যুবকের সঙ্গে যিনি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য এবং বাংলা ভাষার শ্রুতিমধুরতায় আকৃষ্ট হয়ে স্বদেশ থেকে ছুটে এসেছেন আরেক বাংলাপ্রেমিক রাদিচের নিকটে উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে।
আমার জেমস ড্রমন্ড এন্ডার্সন বা জে ডি এন্ডার্সন আবিষ্কার ছিল এক আকস্মিকতার ফল। বলা যায় ঘটনাচক্রেই কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি এবং কেম্ব্রিজের গ্রনভিল এ্যান্ড কীজ কলেজ (এ-কলেজের ফেলো ছিলেন তিনি) আর্কাইভে খুঁজে পাই তাঁর বাংলা সাহিত্যে অবদানের সামগ্রিক সম্ভার। ব্রিটিশ সিভিল সার্ভেন্ট এন্ডার্সন ছিলেন কেম্ব্রিজের অধিবাসী। ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষের বাংলা অঞ্চলের কাছাড়-শ্রীহট্ট এবং চট্টগ্রামে কাটে তাঁর চাকুরিজীবনের অধিকাংশ কাল। চট্টগ্রামের ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর থাকাকালে তিনি রচনা করেন ‘দ্য চিটাগাং প্রোভার্বস্’। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের মতে, ১৮৯৭ সালে কলকাতার সেক্রেটারিয়েট প্রেস থেকে প্রকাশিত এ-গ্রন্থই চট্টগ্রামের প্রবাদ বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ। এন্ডার্সন ছিলেন বঙ্কিম-সাহিত্যের প্রথম অনুবাদক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুহৃদ এই বিদেশিই প্রকৃত অর্থে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে ইউরোপিয় পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা চালান। ১৯১৭ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর লেখা ‘ফনেটিক্স অব দ্য বেঙ্গলি ল্যাংগুয়েজ’ পুস্তিকা এবং ১৯২০-এ, তাঁর মৃত্যুর অল্পকাল আগে ‘এ ম্যানুয়েল অব দ্য বেঙ্গলি ল্যাংগুয়েজ’ শীর্ষক গ্রন্থ। ১৭৮ পৃষ্ঠা সংবলিত বইটির ভূমিকা ১৮ পৃষ্ঠার। বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্যিক গদ্যের নমুনা, নমুনার ইংরেজি ভাষান্তর, শব্দভা-ার এইসব মিলিয়ে এটিকে বাংলাভাষাবিষয়ক একটি প্রতিনিধিত্বশীল গ্রন্থে রূপ দেন এন্ডার্সন। বাংলা লিপির নমুনা দেখাতে গিয়ে এতে তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠির চিত্র তিনি জুড়ে দেন। সেই চিঠিটাই পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথের ‘ছন্দ’ শীর্ষক প্রবন্ধ (সম্বোধন অংশটুকু ব্যতীত) হিসেবে স্থান পায় রবীন্দ্র-রচনাবলির ষষ্ঠ খ-ে। আমার আবিষ্কারের কথা রাদিচেকে জানালে তিনি খুব উৎসাহিত বোধ করেন। তিনি জানান, এন্ডার্সনের কথা শুনেছেন তিনি। জানেন, এন্ডার্সন সুহৃদ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের। এও জানতেন রাদিচে, সরকারি চাকুরি থেকে অবসরের পর থেকে ১৯২০ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এন্ডার্সন ছিলেন কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে বাংলা বিষয়ের শিক্ষক। তাঁর মৃত্যুর পরে আর কাউকে সেখানে নিয়োগ দেওয়া হয় নি। বলা যায় বাংলা বিষয় উঠে যায় কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি থেকে। স্মিত রাদিচে বলেন, তিনি ইংল্যান্ডে থেকেও এন্ডার্সনের রচনাবলির হদিস পান না অথচ আমি সেই সুদূরের অধিবাসী ইংল্যান্ডে এসে আবিষ্কার করি রতেœর খনিÑ একেই বলে মক্কার লোকের হজ¦ না পাওয়া।
নিজের সাহিত্যচর্চা, অনুবাদ, বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ এইসব বিষয়ে আমাদের মধ্যে কথা হয়। প্রসঙ্গত তিনি জানান, কিছুদিন পরেই তাঁর কেম্ব্রিজ যাওয়ার কথা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের
কলম্বিয়া (?) বিশ^বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক কেম্ব্রিজের সাউথ এশিয়ান সেন্টারে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করবেন যেখানে আলোচক হিসেবে থাকবেন তিনি। এসেছিলেন তিনি কেম্ব্রিজে। সেখানে আরও ছিলেন কেম্ব্রিজ বিশ^বিদ্যালয়ের ধর্মতত্ত্ব’র শিক্ষক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসের অনুবাদক চেক বংশোদ্ভূত জুলিয়াস লিপনার যাঁর স্ত্রী অনিন্দিতা বাঙালি। প্রবন্ধপাঠ শেষে প্রশ্ন করেছিলাম, ইউরোপ বর্ষাহীন চার ঋতুর দেশ। রবীন্দ্র ছোটগল্পের অনুবাদক পাঠককে তাঁর গল্পের এই বর্ষা, বর্ষার নানা মাত্রিকতা, ছায়া-ছায়ান্তর, রহস্যময়তা এইসব কিভাবে যথার্থ রূপে পৌঁছে দেবেন। বুদ্ধদেব বসুর রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যবিষয়ক রচনার প্রসঙ্গ এনে তখন রাদিচে বলেছিলেন, রবীন্দ্রগল্পের বর্ষা-প্রতিক্রিয়ার ভাষিক রূপান্তর সম্ভবত ইউরোপিয় ভাষায় ধরা সম্ভব নয়। এও তিনি বলেন, বাংলা ভাষায় আবেগ এবং প্রতিক্রিয়া যতটা উচ্ছ্বাস ও অতিশয়োক্তিতে ভরা ইংরেজিতে সেটা নেই। রাদিচে মধ্যযুগের গীতিকবিতা/বৈষ্ণব পদাবলীর দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন, রবীন্দ্রকাব্যের অনুবাদে এসব বিষয় তাঁকে যথেষ্ট ভাবিত করেছিল। তাছাড়া বাংলা ভাষায় একটা সাংগীতিক সুরেলা ব্যাপার অন্তসলিলা থাকে যেটা ইংরেজিতে নেই, জার্মান ভাষায় নেই, হয়তো ফরাসি কিংবা ইতালিয় ভাষায় আছে। বাংলা ভাষার শক্তি ও মাধুর্য সম্পর্কিত তাঁর বিশ্লেষণ আমাকে মুগ্ধ করে। আমি নিজে কখনও এমনটা ভেবে দেখিনি কিন্তু যখন রাদিচে বলেন, বাংলা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা এবং এর শ্রেষ্ঠত্ব আরও সহজে বোঝা যেতো যদি বাঙালির থাকতো আরব দেশিয়দের মতো তৈলসম্পদ কিংবা জাপানিদের ধনসমৃদ্ধি। থাকলে পৃথিবীর লোকেরা হুমড়ি খেয়ে বাংলা-ই শিখতো যেমনটা তারা শেখে আরবি কিংবা জাপানি। কিন্তু বাংলা ভাষা যারা শিখতে চায় তারা শিখবে ভাষাটার মাধুর্য ও সুষমার প্রেমে পড়ে। আমি আবু সয়ীদ আইয়ুবের কথা বলি। রাদিচের অন্যতম প্রিয় রবীন্দ্র সমালোচক আইয়ুব।
বস্তুত শিক্ষক হিসেবে তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের মত বিদগ্ধ একজন প-িতকে পাওয়াটা ছিল রাদিচের জন্য পরম সৌভাগ্যের। মানুষ হিসেবেও তিনি ছিলেন অতুলনীয়। এখানে বলা যাবে, যুবক বয়স থেকেই ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ জন্মে তাঁর। আর অক্সফোর্ডে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে তাঁর চাইতে মাত্র এক বছরের বড়ো বিখ্যাত সুকান্ত চৌধুরীর সঙ্গে। সুকান্ত ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের শিক্ষার্থী। বর্তমানে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী সুপ্রিয়া দু’জনেই কলকাতা যাদবপুর বিশ^বিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ইমেরিটাস অধ্যাপক। এই পরিবারের সংস্পর্শ তাঁর জীবনের এক বিরাট পাথেয় ছিল। সুকান্ত চৌধুরীর বাবা কান্তিপ্রসাদ চৌধুরী এবং মা সুজাতা চৌধুরীর জীবনটাও ছিল উল্লেখ করবার মতোন। সুজাতাও ছিলেন যাদবপুর বিশ^বিদ্যালয়ের অধ্যাপক। সুকান্ত’র কলকাতার সল্টলেকের বাড়িতে বেড়াতে এলে বাড়ির সকলেই তাঁর সঙ্গে বাংলায় কথা বলতেন এবং অনেকটা বাধ্যতই তিনিও বাংলা বলার চেষ্টা করতে থাকেন। এভাবেই বাংলার সাহচর্য হয়ে যায় তাঁর পরিণতি। এখানে একথাও বলা দরকার, বাঙালি নারীর কড়ি ও কোমল উভয় রূপের পরিচয় তিনি পেয়েছিলেন সুকান্ত চৌধুরীদের পরিবারেই। সুকান্ত’র মা সুজাতা চৌধুরী (১৯১৩-২০০৩) যে-বছর মৃত্যুবরণ করেন সে-বছর ২০০৩ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি সংঘটিত হয় ইতিহাসের সেই ভয়ধরানো গুজরাট দাঙ্গা। সুজাতা মারা যান ১১ ফেব্রুয়ারি। ৫০০ লোকের উপস্থিতিতে শাহীবাগে শাহজাহানের প্রাসাদসংলগ্ন খোলা জায়গায় বক্তৃতা করেন রাদিচে। এখানেই এই আহমেদাবাদে ১৮৭৮ সালে ১৭ বছর বয়সী রবীন্দ্রনাথ বেড়াতে আসেন তাঁর সরকারি চাকুরে বড়ো ভাইয়ের বাসভবনে এবং কাটিয়ে যান ৪ মাস। পরবর্তীতে ‘জীবনস্মৃতি’ এবং ‘ছেলেবেলা’য় সেকথা স্মরণ করেন তিনি। এটাও আমরা জানি, ‘ক্ষুধিত পাষাণ’ গল্পের মালমসলা হলো এই চার মাসের রবীন্দ্রনাথের আহমেদাবাদ-বাস। সুজাতার স্বামী কান্তিপ্রসাদ মৃত্যুবরণ করেন ১৯৮৩ সালে। রাদিচে সুকান্তদের সল্টলেকের বাড়িতে আসেন ১৯৭৬ সালে। সে-হিসেবে তাঁর প্রত্যক্ষ বাঙালি পরিবার ও সমাজের সংযোগের বয়স দাঁড়ায় ২৫ যার অর্থ জীবনের দুই-তৃতীয়াংশ কাল তাঁর কাটে বাঙালিস্পৃষ্টতায়। ১৯৭৬ সালেই রাদিচে সুকান্তদের বাড়িতে থাকাকালে রবীন্দ্রনাথের বেশকিছু কবিতার অনুবাদ বিষয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করেন। ১৯৮৫ সালে সেসবের একটি সংকলন প্রকাশিত হয়। সেই গ্রন্থের নির্ঘণ্ট প্রস্তুতের সময় সুজাতা চৌধুরীর সহায়তা পান তিনি যেটা তিনি স্বীকারও করেন। বিভিন্ন ফুল, পাখি, বাংলার প্রকৃতির অনুষঙ্গ ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে গিয়ে প্রত্যক্ষ বাঙালি-অভিজ্ঞতার উৎস হিসেবে পান তিনি সুজাতাকে। এরপর ১৯৮২ সালে রাদিচে তাঁর দুই কন্যা (বড়োটির বয়স ২ বছর এবং ছোটটির ৭ মাস) ও স্ত্রীকে নিয়ে কাটিয়ে যান চৌধুরী পরিবারে। ২০০১ সালের মার্চ-এপ্রিলেও কয়েকটা দিন তিনি কাটান তাঁদের সঙ্গে। ২০০০ সালে কলকাতার ‘প্যাপিরাস’ থেকে বেরোয় সুজাতা চৌধুরীর লেখা স্মৃতিকথা ‘মনে আছে’। সেখানে খুব আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন উইলিয়াম রাদিচের সঙ্গে তাঁদের পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা। এটা বোঝা যায় রাদিচে’র বাঙালি-অনুধ্যান সুজাতা ও তাঁর পরিবারের সংস্পর্শ ছাড়া এতোটা বহুমাত্রিক হওয়া সম্ভব ছিল না। সুজাতা লেখাপড়া করেন আসামের গোহাটি কলেজ, কলকাতার স্কটিশ চার্চ ও প্রেসিডেন্সি কলেজে। তেমনি শিক্ষকতার ক্ষেত্রেও বিচিত্রতা তাঁর বৃত্তান্ত। আশুতোষ কলেজ, লেডি কিন কলেজ (শিলং), গোকুল দাস কলেজ (মুরাদাবাদ) ছাড়াও আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতা করেন ৫ বছর। শিলং-এ থাকাকালে নিয়মিত লন টেনিস খেলতেন সুজাতা চৌধুরী। বাঙালি রমণির টেনিস খেলা সেসময়টাতে বেশ সাড়া তুলেছিল। এল. বি. কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, বেথুন-এ দুই যুগের অধ্যাপনা ছাড়াও বিখ্যাত লেডি ব্যাব্রোন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হিসেবে নিযুক্তি এই মহিয়সী বাঙালি নারীত্বের দৃঢ়তার সত্তাকে পূর্ণবিকশিত করেছিল। সুজাতা ও কান্তিপ্রসাদের বিবাহ সম্পর্কিত ঘটনাটিও সেসময়কার কলকাতায় জন্ম দিয়েছিল প্রভূত হৈচৈয়ের। পাত্র কান্তিপ্রসাদ ছিলেন ব্রাক্ষ্মণ এবং পাত্রী সুজাতা ব্রাক্ষ্ম। এই অসম সংযোগের ব্যাপারটাকে ইতিবাচকভাবে দেখতে গররাজি ছিল তৎকালীন সমাজ। কিন্তু সমস্ত প্রতিকূলতাকে এড়িয়ে তাঁরা পারস্পরিক ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধের মূল্যকে সর্বাধিক গুরুত্বে বিবেচনা করেছিলেন। কাজেই এক বিচিত্র জীবনেতিহাসের যবনিকা উন্মোচিত হয়েছিল বাঙালি জীবনের অভিজ্ঞতা¯œাত রাদিচের দৃষ্টিপটে।
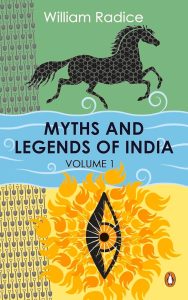
আবার বাংলাদেশে ড. মনিরুজ্জামান পরিবারের সাহচর্য রাদিচেকে বাংলার পূর্ব দিককার মেজাজ ও আবহকে বুঝতে সাহায্য করে। রবীন্দ্র কাব্য কিংবা রবীন্দ্রনাথের ‘তাসের দেশ’ ‘ডাকঘর’ নাটক অনুবাদের পাশাপাশি তাঁর ছোটগল্পের অনুবাদের বিষয়টা ভাবনায় রেখে বিচার করলে রাদিচের এই দুই বাংলার অভিজ্ঞতার প্রায়োগিকতাকে বুঝতে পারা যায়। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের দশ/বারোটি ছোটগল্পে রয়েছে পূর্ববঙ্গের জীবন, সমাজ, প্রকৃতি ও লোকাচারের পরিপ্রেক্ষিত। মনিরুজ্জামানের স্ত্রী হাসিন জাহান ছিলেন একই সঙ্গে স্কুল-শিক্ষয়িত্রী এবং একটি বাঙালি পরিবারের সার্বক্ষণিক পরিচালনাকারী। সাধারণ ধর্মপ্রাণ-সংস্কৃতিবান-শিক্ষিত হাসিন ছিলেন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ এবং ভাষাবিজ্ঞানী ঢাকা বিশ^বিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ড. মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের কন্যা। রাদিচে খুব সহজেই আন্তরিকতার সঙ্গে মানুষের সঙ্গে মিশতেন। সাধারণ ইংরেজ পরিবারের মধ্যে যে-উন্নাসিকতা ও আভিজাত্যের গৌরববোধ (নেতিবাচক অর্থে নয়, বৈশিষ্ট্য বোঝাতে) রাদিচের মধ্যে ছিল অনুপস্থিত। আমার ব্যক্তিগত ধারণা তিনি তাঁর স্বজাতির সেই বিশেষত্বকে বিসর্জন দিতে শিখেছিলেন তাঁর কলকাতার পূর্ববাসেই। তাছাড়া তাঁদের আদিপুরুষ ইতালিয়দের মিশুক স্বভাবের খানিকটা শেকড়সংযোগ পেয়ে থাকবেন তিনি উত্তরাধিকারসূত্রেও। তাঁর সহজসরলতা ও মিশুক স্বভাবের একটি দৃষ্টান্ত মনে পড়ে। মনে পড়ে তাঁর চট্টগ্রামে থাকাকালীন একটি ঘটনার কথা। চট্টগ্রাম শহরের আগ্রাবাদে ‘জোহরা ম্যারেজ হল’-এ (পরবর্তীতে ‘মিষ্টিমুখ’-এর বিক্রয়কেন্দ্র) আমরা তাঁকে নিয়ে যাই বাংলা বিভাগের প্রবীণতম কর্মকর্তা আবদুর রশীদের মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে। “আমি কখনও বাঙালি ললনার বিবাহ দেখিনি” বলেই অনুষ্ঠানস্থলে সোৎসাহে পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন বিবিধ উপলক্ষ্য এবং তাঁর ক্যামেরায় ধারণ করে চলেন একের পর এক ছবি। অকস্মাৎ তিনি ঢুকে পড়েন অন্দরমহলে যেখানে ছিল না কোনো পুরুষ সদস্য। আমি বাইরে কারো সঙ্গে কথা বলছিলাম। অকস্মাৎ কানে আসে ‘আস্তাগফিরুল্লাহ্’ আরবি শব্দে পৌণঃপুণিক নারীকষ্ঠ উচ্চারণ। ঝটিতি গিয়ে দেখি রশীদ সাহেবের কন্যা-পাত্রীকে ঘিরে মহিলারা একটি পরিবেষ্টনী তৈরি করে খানিকটা শোরগোলে মত্ত। আমার পেছন-পেছন মনিরুজ্জামান স্যারও দৌড়ে আসেন এবং সবাইকে বোঝাতে থাকেনÑ “ইনি উইলিয়াম রাদিচে, বিদেশি। কখনও বাঙালি বিয়েতে যাননি, তাই উৎসাহ নিয়ে দেখছেন।” পরে সেই পাত্রী, পাত্রীর আত্মীয়স্বজনসহ আমরা সহকর্মীরা রাদিচের সেই ক্যামেরাচিত্রের বিষয়বস্তু হয়ে পড়ি অনায়াসে। ক্যাম্পাসেও তিনি মিশতেন এবং কথা বলতেন অনেকের সঙ্গে।

আমাদের শিক্ষক লাউঞ্জের এক কর্মচারি ছিল বেলাল যার নাম। যুবকবয়সী বেলালকে একদিন অদূরের টেবিলস্থিত চিনির বাটি দেখিয়ে রাদিচে বলেন: “বেলাল ভাই, আমি কি ঐ চিনিটা পেতে পারি?” বেলাল প্রথমটায় বুঝতে না পেরে খানিকটা হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকে। পাশের টেবিল থেকে আমি বুঝিয়ে দেই তাকে: ওনার চায়ে আরেকটু চিনি লাগবে। কিছুদিন পর রাদিচে স্বদেশে ফিরে গেলে একদিন বেলাল আমার কাছে জানতে চায়Ñ আপনাদের ডিপার্টমেন্টে যে আসছিল সেই বিদেশি ভদ্রলোকটা কোথায়? বললাম, দেশে ফিরে গেছেন। তখন বেলাল বলে, উনি এত শান্ত আর অনুচ্চ স্বরে কথা বলতেন যে কর্কশতা ও চিৎকার অভ্যস্ত আমাদের সেটা বুঝতে অনেকটা সময় লেগে যেতো। বস্তুত বাঙালি জীবনে কেবল মেশার কারণে মেশেননি তিনি, কিংবা তাঁর নিজস্ব অনুবাদকর্মের সুবিধার জন্যেও ছিল না তাঁর সেই আগ্রহ। বরং সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি জাতি ও সংস্কৃতির বিবিধ অনুষঙ্গকে জানবার ও বুঝবার অধ্যবসায়ই ছিল সেখানে মুখ্য। সেই যে তিনি বলেছিলেন, অল্প বয়সেই ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তিনি একটা টান অনুভব করতেন। সেই ভারতবর্ষের একেবারে পূর্ব প্রান্তিকতার মানুষ, যে-মানুষকে দেখা গেছে ‘পোস্টমাস্টারে’,
কিংবা যে-মানুষদের দেখা গেছে ‘সমাপ্তি’ কি ‘শাস্তি’তে তাদের হাজার বছরবাহিত জীবনটা আসলে কেমন সেটাই রাদিচে পর্যবেক্ষণে ও অনুভবে ব্যস্ত ছিলেন।
বাংলা ও ইংরেজির সেতুবন্ধনের ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতা প্রশ্নাতীত। স্পেনিয় ভাষার মার্কেজের ইংরেজি অনুবাদক গ্রেগরি রাবাসা, জার্মান গুন্টার গ্রাসের অনুবাদক কার্ল ম্যানহাইমের মতোন বাংলা থেকে ইংরেজি ভাষান্তরের ক্ষেত্রে রাদিচের নামটিও থাকবে জ¦লজ¦লে। ভাষান্তরের অভিযাত্রাপথে যে-সামগ্রিক জীবনসাধনাকে তিনি কাজে লাগান বাঙালির ইতিহাস সমাজ সংস্কৃতি ও জীবনটাকে বুঝতে তার পরিণতি নিঃসন্দেহে অর্জনের নক্ষত্র হয়েই বিরাজমান হবে দীর্ঘকাল। কেবল যে অনুবাদের মধ্য দিয়েই তিনি মধুসূদন রবীন্দ্রনাথের জগতটাকে হৃদয়ঙ্গম করবার চেষ্টা করেন তা নয়, বাঙালির জীবনবৃত্তের মাহাত্ম্যকে নানা দিক থেকে ছুঁয়েছেনে দেখেছেন তিনি। ৭৮৪ পৃষ্ঠার এক বিস্ময়কর গ্রন্থ তাঁর ‘মিথস্ এ্যান্ড লিজেন্ডস্ অব ইন্ডিয়া;। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম, জৈন, সিরিয় খ্রিস্টান এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির জীবনের প্রতিফলনে রচিত এসব কাহিনীর মধ্য দিয়ে উঠে আসে এমন এক ভূখন্ডের ছবি যা এর হাজারও বৈচিত্র্য নিয়ে টিকে রয়েছে বিশ^সভ্যতায়। তাঁর আরেকটি গ্রন্থের কথা বলা যায় যেটির মাধ্যমে তিনি ভারতবর্ষের এক বিপুল জনগোষ্ঠির মানস-পরিবর্তনের ইতিহাসটাকে চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ করেনÑ ‘স্বামী বিবেকানন্দ এ্যান্ড দ্য মডার্নাইজেশন অব ইন্ডিয়া’। ১৯৯৩ সালে স্বামী বিবেকানন্দের বিশ^ধর্ম-সম্মেলনে শিকাগো বক্তৃতার শত বছর উদযাপন উপলক্ষ্যে লন্ডনের ‘সোয়াস’-এ যে ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয় সে-উদ্দেশে রচিত প্রবন্ধসমূহের এ সংকলন উইলিয়াম রাদিচের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯৮ সালে অক্সফোর্ড ইউনিভিার্সিটি প্রেস থেকে। পরবর্তীতে গ্রন্থটির একাধিক সংস্করণ হয়। বস্তুত বাঙালির জীবনের সামগ্রিকতাকে জানাবোঝার রাদিচে-অধ্যবসায়ের দারুণ পরিণতি তাঁর কৃত সাহিত্যিক অনুবাদকর্মগুলো। তা সে মধুসূদন কিংবা রবীন্দ্রনাথের কাব্য, ছোটগল্প, নাটকই হোক কিংবা হোক অন্যতর প্রকাশনা। বাংলা ভাষার অনুবাদে তাঁর সাবলীলতা এবং স্বতস্ফূর্ততা বিশেষভাবে লক্ষ করবার মতোন। ১৯২২ সালে রচিত রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত ‘তালগাছ’ কবিতাটির রাদিচেকৃত অনুবাদের খানিকটা লক্ষ করা যাক-
Palm-Tree: single-legged giant,
Topping the other trees,
Peering at the firmament—
It longs to pierce the black
Cloud-ceiling and fly away, away,
If only it had wings.”
কিশোর-মনের স্বপ্নচারিতা ও কৌতূহলস্পৃষ্ট ভাবনার প্রতিফলনে রাদিচের অনুবাদ সফলতা পায় শব্দান্তরের প্রকৃত সক্রিয়তায়। ১৯০৩ সালে রচিত ‘বীরপুরুষ’ কবিতাটির দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। এটিও বহুলপঠিত এবং পাঠ্যবইয়ের জন্য সুনির্বাচিত একটি কবিতা-
Say we made a journey, mother,
Roaming far and wide together—
You would have a palanquin,
Doors kept open just a chink,
I would ride a red horse, clip
Clop-clip along beside you, lfting
Clouds of red dust with my clatter.”
অনুবাদক রাদিচের জগতের বিচিত্রতার মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তাঁর বন্ধু সুকান্ত চৌধুরীর কথা স্মরণ করতে হয়। ইতঃপূর্বে সুজাতা চৌধুরীর প্রসঙ্গ উঠেছিল। ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ডে লেখাপড়া ও উচ্চশিক্ষার কৃতিত্বপূর্ণ ফল-লাভকারী সুকান্ত চৌধুরী এবং তাঁর স্ত্রী বর্তমানে কলকাতার যাদবপুর বিশ^বিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক। প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষকতায় কাটান দেড় যুগ। এছাড়া অক্সফোর্ডের বিখ্যাত অল সৌলস্ কলেজ, কেম্ব্রিজের সেন্ট জন্স কলেজ, আলবার্টা, ভার্জিনিয়া, লয়োলা ইউনিভার্সিটির ফেলো হিসেবে কাটান নানান সময়ে। শেক্সপিয়র, এলিজাবেথিয় কবিতা, রেনেসাঁ-যুগ এইসব নিয়ে তাঁর রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাকর্ম। রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম, শরৎচন্দ্র, সুকুমার রায়, রাজশেখর বসু প্রমুখের রচনা ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেছেন তিনি। এডওয়ার্ড লিয়রের সমস্ত লিমেরিকের বঙ্গানুবাদ করেছেন তিনি। মূল ইতালিয় ভাষা থেকে অনুবাদ করেছেন লিওনার্দো দা ভিঞ্চির ‘নোটবুক’। কাজেই এরকম একজন অসাধারণ প্রতিভাবান ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের সাহচর্য উইলিয়ম রাদিচের জন্য এক ধরনের আশীর্বাদ হয়ে দেখা দেয়। বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে সেকথার উল্লেখ করতে ভোলেন না স্বয়ং রাদিচেও।
‘পরবাস’ নামক পত্রিকায় প্রকাশিত উইলিয়াম রাদিচের একটি রচনার খানিকটা (মদীয় অনুবাদে) লক্ষ করি যেখানে তিনি বলছেন: “আমার দারুণ সৌভাগ্য, শেখা এবং অধ্যয়নের জন্য আমি বাংলাকে বেছে নিয়েছিলাম। বাঙালিরা সর্বোচ্চ বিবেচনায় খুবই চমৎকার মানুষ। পৃথিবীতে তারা কোনো ক্ষতিসাধনের কাজ করেনি। আর, আধুনিককালে তাদের সংস্কৃতি বেশ কয়েকজন অসাধারণ মেধাবী ব্যক্তির জন্ম দিয়েছে।” যতবার তাঁকে দেখেছি ও তাঁর সঙ্গে সময় কাটিয়েছি আলাপচারিতায়, কখনও তাঁকে চড়া গলায় কথা বলতে শুনিনি। মনে হয়েছে কণ্ঠস্বরকে উচ্চগ্রামে তোলার ব্যাপারটাই তাঁর ধাতে ছিলনা। এও কি তাঁর দীর্ঘকালীন মার্জিত বাঙালি মানুষজনের সঙ্গে মেলামেশা ও অভ্যেসের ফল! হতে পারে। তবে রাদিচে তাঁর সারাজীবনে সবচাইতে বেশি অনুসরণ করে গেছেন এক পরিশীলিত রবিরেখা। এমনকি তাঁর স্বরচিত কবিতা যেখানে তিনি তাঁর স্বকীয় ভাষা-সংস্কৃতিতে অবারিত সেখানেও পরশ বুলিয়ে যান রবীন্দ্রনাথ। স্বয়ং রাদিচে সেকথা কবুল করে তাঁরই ‘দ্য রিট্রিট’ কাব্যগ্রন্থের কবিতাকে উপস্থাপন করেন তাঁর সেই রবিঋণ বোঝাবার জন্য। কবিতাটি লক্ষ করা যেতে পারে-I’m painting a fence,/ Listening to a bird./ Plane flies over:/ Bird can’t be heard.// If all the planes in the world/ Shared the same space,/ And all the birds in the world/ Were in the same place,// Which would be louder?/ The singing or the roar?/ It should be the birds,/ But I’m not quite sure.উইলিয়াম রাদিচে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং রবীন্দ্রনাথের আশ্রয়ে বাংলাকে ভালোবেসে পরিচালনা করেছিলেন তাঁর কর্মজীবনকে। ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত তাঁর বাংলা ভাষা শিক্ষার গ্রন্থ ‘টিচ্ ইউরসেল্ফ বেঙ্গলি’ লক্ষ করলে বোঝা যায় বাংলা ভাষাকে তিনি কতটা গ্রহণ ও উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ২০০৩ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ দশ বছরের কিছু কম সময়ের মধ্যে রাদিচের এ-গ্রন্থের ১৭টি মুদ্রণ হয়েছে, সামনের দিনে হয়তো আরো হবে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত দিয়ে শুরু রাদিচের যাত্রা রবীন্দ্রবাহিত হয়ে বহু মাত্রায় রূপ নিয়েছিল। একজন বিভাষী-বিদেশি মানুষের এমন সাফল্য অনুপ্রেরণামূলক তো বটেই, অনুসরণযোগ্যও।
মহীবুল আজিজ, প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়







