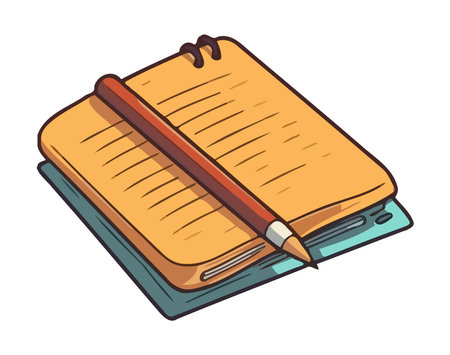মোশতাক আহমদ
সাফায়েতের ঘটনা
আজ ছুটির দিন। সকাল দশটায় তার ঘুম ভাঙল মাথার বাম দিকে সিঁথি বরাবর ঝিঁ ঝিঁ লাগার অনুভূতি নিয়ে। হ্যাঁ, ঝিঁ ঝিঁই বটে; পায়ে মাঝে মাঝে যে রকম ঝিঁ ঝিঁ ধরে। আজ ঘুম ভাঙার পরেও একটা প্রাচীনা আলস্য সিন্দাবাদের দৈত্যের মতো ভর করলো তার ঘাড়ে। ডান পাশ ফিরে শুলো আরো আধ ঘন্টার জন্য। সে শুয়ে আছে, অকর্মক। তার ক্রিয়াকলাপগুলো বর্ণনা করতে অপারগ অতএব। এ মুহূর্তটি খুবই সম্ভাবনাময়। আমরা জানি না যার কথা বলছি (গল্পের মূল চরিত্র) সে আজ কী করবে বা আদৌ কী করে থাকে সে। এমনকি তাকে আমি কখনো চিনলেও জীবন তো অগাধ, হয়তো তার জীবন কিংবা রুটিন বদলে গেছে। ছুটির দিনের কথা যখন বলা হয়েই গেছে, সে তাহলে চাকরিজীবী হোক। আর আলস্যের ধরন-ধারণ থেকে তাকে বাঙালি লেখক (বা.লে.) শ্রেণিতে রাখা যাক, আমার লিখতে সুবিধা হবে। ধরা যাক সে একজন গল্পকার, আজ তার একটা গল্প লেখার অবকাশ আছে।
ছয় মাস আগে হঠাৎ করেই সে একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষী গল্প লিখে ফেলল। গল্পের একটা কপি পাঠিয়ে দিলো জনপ্রিয় জাতীয় দৈনিকের সাময়িকী বরাবর, আরেক কপি পাঠিয়ে দিল প্রিয় পরিচিত একজন গল্পকার বরাবর। গল্পের নায়ক ছিল একজন কবি। নায়কের নামটি পুরনো একজন বন্ধু রাশিদুল আনোয়ারের নাম অনুসরণে নেওয়া হয়েছিল, কেননা নামটি কবিসুলভ মনে হয়েছিল। রাশিদও তো কবিই ছিল। মাসখানেকের মধ্যে কাইয়ুম চৌধুরীর ইলাস্ট্রেশনসহ গল্পটি মহাসমারোহে ছাপা হয়ে যায়।
জনপ্রিয় জাতীয় দৈনিকে গল্প ছাপা হয়ে গেছে; এর পর তো ঘটনার ঘনঘটায় আমরা গল্পের মূল চরিত্রটির দিকে ফিরে তাকাবার সুযোগই পাব না। এই ফাঁকে সংক্ষেপ রেখাচিত্রে তাকে এঁকে ফেলা যাক। সে একা, অনেকটা প্রশান্ত মহাসাগরে অস্ট্রেলিয়ার একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপ যেনবা, কিন্তু সুজলা সুফলা। বন্ধুরা সব ‘অতীত দিনের স্মৃতি’, প্রকৃতপক্ষে তার কোনও বন্ধু নাই। তার হাহাকারগুলো বন্ধুহীনতার, স্বপ্নহীনতার, স্মৃতিহীনতার; আশঙ্কা হয় যেনবা ভবিষ্যৎহীনতার। বাংলাদেশের একটি শহরে সে একটি ‘অমল ধবল চাকরি’ নিয়ে একাকী জীবনযাপন করে আসছে।
রাশিদের ঘটনা
জীবনের প্রথম সাতাশ-আটাশ বছর পর্যন্ত সে ছিল আপাদমস্তক একজন কবি। সে, রাশিদুল আনোয়ার আমার বন্ধু ছিল। ইমেইলের যুগে এখনো সে আমাকে মাঝে মাঝে ইনিয়ে বিনিয়ে চিঠি লিখে থাকে; নিয়ম করে ছ মাসে একটা, কুরিয়ার সার্ভিসে। তাঁর চিঠিগুলো থেকে চুরি করেই আমি এই গল্পখানা দাঁড় করালাম কিনা, সেহেতু তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়তোবা দরকার; অবশ্য মাইন্ড করার ব্যাপারটা তাঁর মধ্যে ছিল না। তাঁর চিঠিতে লেখা/ না-লেখার বিষয়গুলো এতখানি জায়গা জুড়ে থাকে যে, তাঁর জবাবে কবিতা লেখার জন্য নিয়মিত প্রেরণা দেওয়া ছাড়া আর বছরে একবার আমার লিটলম্যাগের জন্য লেখা চেয়ে তাগাদা দেয়া ছাড়া আমিও আর কোনও ব্যাপারে খোঁজ খবর করতে দ্বিধাগ্রস্ত থাকি। আমার চিঠি পেলে সে এখনো খুব অনুপ্রাণিত হয়, ক্যাম্পাস জীবনের মতো। সে যে আর লেখে না এই কথাটি সে গত দশ বছরে আমার কাছে একবারও কবুল করেনি। আমার কাছে হয়তোবা সে আজীবন কবি হয়েই থাকতে চায়। “লিখি বললে ভুল বলা হবে, আবার লিখি না বললেও আত্মসম্মান থাকে না” ক্যাম্পাসের এক জনপ্রিয় কবি কয়েকবছর পার্বত্য চট্টগ্রামের এক উপজিলায় চাকুরি করে এসে সরল স্বীকারোক্তি করেছিলেন এইভাবেই।
তো, সাতাশ-আটাশের পর রাশিদুলের অন্য জীবন শুরু হয়েছে।
সাফায়েতের গল্প ছাপা হবার পর আরো কি কি হলো
আমাদের এই গল্পকার, সাফায়েত জামিল এক সময়ে ক্যাম্পাস জীবনে লেখালেখি করত। প্রথমেই তার মনে হল ক্যাম্পাসের বন্ধুদের এই দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হওয়াটা জানান দেয়া প্রয়োজন। ‘জীবন চলিয়া গিয়াছে কুড়ি কুড়ি বছরের পার’; – কুড়ি নয়, মোটামুটি দশ বছর যাবত অধিকাংশ বন্ধু-বান্ধবের কুশল সংবাদ জানে না সে। সে গোটা দশেক এসএমএস পাঠালো দশ জন বন্ধুর কাছে। ভাষ্য একটাই, আজ অমুক পত্রিকায় আমার গল্প ছাপা হয়েছে, কেমন লাগল পড়ে জানাও।
এর পরের আটচল্লিশ ঘন্টায় কিছু ফিরতি-এসএমএস আসে এবং কিছু ফোনালাপ হয় মুঠোফোনের দৌলতে।
রোমেল: গল্পটা পড়লাম। দারুন হয়েছে! কবে লিখলে? (অবশ্য আয়রনি এই যে, পরবর্তী গল্প ছাপা হবার পর মন্তব্য ছিল- বরাবরের মতো কিছুই বুঝলাম না। তবুও অভিনন্দন!)।
হেলাল: ‘হন্তারক’ পড়েছি। তোমার গল্পের চরিত্রটি কি আমাদের বকুল নাকি? আমি খুব খুশি যে আমাদের বন্ধু এখনো লিখছে এবং ক্যাম্পাস- স্মৃতি তাকে তাড়িত করে।
শুভ্রা এসএমএস পেয়েই কলব্যাক করে জানায়, সে গল্পটি পড়বে। সে জানত না গল্পকারের বর্তমান অবস্থান। কথা এগোতে পারেনি গল্পকারের মুঠোফোনের ইয়ারপিসের যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে।
পিয়াল (টেলিফোনে): গুরু, তোমার এসএমএস পাওনের আগেই সকালবেলা উইঠ্যাই গল্পটা পইড়া ফেলছি …! কেমনে বুঝলাম তোমার লেখা কীনা?- আবার জিগায়!
মিসিগান প্রবাসী রুমী গল্প পড়া অবধি খুবই উদ্বিগ্ন ছিল। কেননা গল্পের নায়ক আত্মঘাতী হয়েছিল। রুমী দশ বছর যাবত বন্ধুর কোনও খবর জানে না বলে গল্পের চরিত্রের মানসিক অবস্থার সাথে বন্ধুর মানসিক অবস্থা মিলিয়ে ফেলে এবং একে ওকে ফোন করে গল্পকারের ফোন নাম্বার সংগ্রহ করার পর এক দুপুরে দীর্ঘ সময় আলাপ করেছিল।
সুমন: লেখাটা চোখে পড়েছিল অনলাইনে। কিন্তু ভেবেছিলাম তুমি লেখালেখি ছেড়ে দিছো, এইটা অন্য কারো লেখা।
রেজা: লেখার জন্য তোমাকে কত টাকা সম্মানী দিলো?
জিললুর: তোমার গল্পের শেষটা তাড়াহুড়ো করে ফেলেছ এবং পরিণতিটা আরোপিত মনে হয়েছে। তবে লেখাটিতে যথেষ্ট নিরীক্ষা রয়েছে। ক্যারি অন!
নূর মোহাম্মদ গল্পের ভালোমন্দ বিচারে না গিয়ে ফিরতি মেসেজ হিসেবে একটা আরবিতে লেখা নির্দেশনা পাঠিয়ে সেটা আরো দশজনকে পাঠাতে অনুরোধ করে। এতে জাগতিক ও পারলৌকিক উন্নতির নিশ্চয়তা জানানো ছিল। গল্পকারকে অগত্যা ভদ্রভাবে ধর্মীয় কুসংস্কার বিষয়ে তার নিস্পৃহতার কথা জানাতে হল (তবে তার বিশ্বাসের প্রতি পূর্ণ সম্মানের কথা জানিয়ে দিল)। নূর মোহাম্মদ এতে অপ্রস্তুত বোধ করে এবং জানায়, সে অন্যের একটা মেসেজ কনভে করেছে মাত্র।
শুধু গল্পকেন্দ্রিক নয়, অনেকের সাম্প্রতিক ও পারিবারিক খোঁজ খবরও পাওয়া গেল। আদিব হাসানের সাথে ছয় বছর আগে একটা বিদেশি তেল কোম্পানিতে ইন্টার্ভিউ দিতে গিয়ে দেখা হয়েছিল; সে এখনো তেল কোম্পানিতে আছে। ‘মামু’ নামে সমধিক প্রসিদ্ধ দিদার একদিন মাঝ রাতে ফোন দিল, তার আট বছরের পুত্রধন নাকি লেডিকিলার হয়ে গেছে। গল্পকার শাহাদুজ্জামানের একটি সুতন্বী ফন্টে ছাপা চিঠি এলো দিন দশেক পর-তোমার লেখাটি বেশ হয়েছে, পত্রিকায় ছাপাও হয়েছে দেখতে পেলাম। ভাষাগত ব্যাপারগুলো লিখতে লিখতে আয়ত্তে এসে যাবে। লিখে যাও।
এভাবে একটি গল্প ছাপা হওয়ার সুবাদে এবং মুঠোফোনের দৌলতে আমাদের গল্পকারের বন্ধু-বান্ধবদের সাথে একটি রিইউনিয়নের আমেজ সৃষ্টি হল। এর ফলে তার মধ্যে আরও লেখার উৎসাহ জাগল। কিন্তু গল্পের প্লটে অগ্রজ লেখকগণ যেভাবে সাধ্যমতো ঘরবাড়ি তুলে গেছেন তাতে গল্পের প্লট জমির প্লটের চেয়েও দুর্লভ আজকাল।
আবিদের ঘটনাই বটে
এক যুগ আগে, সোভিয়েট-পতনে ওর তরুণ স্বপ্নচারী হৃদয় যেরকমভাবে ভেঙেচুরে গিয়েছিল, আজ আবার সেই ধরনের অনুভূতি নিয়ে বাড়ি ফেরে আবিদ জাফর। সে ভেবেছিল, ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ার লুকোচুরি দেখার ফাঁকে ফাঁকে গরিব মানুষগুলোর কিছুটা কাজে আসবে সে, গরিব মহিলাদেরও কিছুটা ক্ষমতার অধিকারী দেখতে পাবে। এই নিয়ে জীবনের তৃতীয় রোমান্টিসিজম ধরা খেয়ে যায়।
খুব পছন্দ ও কৌতূহলে এনজিওর চাকরি নিয়ে কিছুদিন দেশের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ায় আবিদ। বন্ধুরা মজা করে ডাকে ‘আবেদ’, কেননা ফজলে হাসান আবেদের মতো আত্মনিবেদন যে! আমরা ওকে ‘আবিদ’ই বলব। জীবনের দ্বিতীয় রোমান্টিসিজম মিসমার হয়ে যাবার পর এনজিওর চাকুরিটাকে সে অবলম্বন করে নেয়। শুধু চাকরি না- এ তার জীবন, এ তার দর্শন। আবিদের জীবনের প্রথম রোমান্টিসিজম ছিল ক্যাম্পাসকেন্দ্রিক বাম রাজনীতি, সেই সূত্রে সোভিয়েত-সমগ্র। দ্বিতীয়টার (একটু পরে সবিস্তারে জানাচ্ছি) গুরুত্ব কতখানি ছিল, সেটা আজ রেট্রোস্পেক্টিভ ছবি দেখার মতো করে ভাবতে বসার অবকাশ আছে তার।
নাকি রাশিদের জীবনেও একই ঘটনা ঘটেছিল!
রাজনীতি আর রোমান্টিসিজমকে আলাদা করতে পারেনি আবিদ জাফরের বন্ধুবান্ধবেরা। আবিদ জাফর হয়তোবা হয়ে উঠেছিল রোমান্টিক বিপ্লবী (একই সাথে আপাত নিস্পাপ এবং চরম দুটি শব্দবন্ধের বিশেষণ ছিল এই প্রজাতি বা প্রজন্মের)। তবে সকলের কথা নয়, ওর একার কথাই হোক। ওর স্বভাবের মধ্যে চিরকাল একটা প্রতিরোধ ছিল। স্বপ্নজীবী কৈশোর, উথালপাথাল বয়ঃসন্ধি, কত সব মারাত্মক সময় পেরিয়ে এসেছে সে ওই প্রতিরোধের গুণে। ওর এরকম একটা অহংবোধ ছিল কোনো মেয়েকে (নারীকে) কোনোদিন ভালোবাসবে না, কারো হাসি বা কটাক্ষ তাকে দুর্বল বা বিচলিত করবে না। যথেষ্ট কারণ ছিল ওর এরকম দৃঢ়তার :
ক) বৃষ্টির রাতে জানালার পাশে কে যেন একজন এসে দাঁড়ায় ভেনাসের ধরনে, ওকে অহঙ্কারের যুদ্ধে রসদ জোগায়;
খ) ভোরবেলা ঘুম ভেঙে বারান্দায় এসে দাঁড়ালে বাগানের সব ফুল কেমন করে যেন একক, অস্তিত্বে ফুলেশ্বরী সেজে চিবুক নুয়ে দাঁড়ায় ওকে অহঙ্কারের যুদ্ধে ঋজুতা দেয়;
গ) মাঝরাতে বন্দরনগরী অন্ধকারে ডুবে গেলে নিজেকে যখন নিমজ্জিত বলে মনে হতে থাকে, সে সময় কেউ এসে ওর উজ্জ্বল উদ্ধার হয়। এরকম এক অশরীরী (আবিদের পছন্দের শব্দ ‘অবয়বহীন’) মানবীর (আবিদের মনে হতো ‘স্বপ্নেশ্বরী’) প্রেম নিয়ে পৃথিবীতে মানুষের যৌবনকাল ছুঁয়েছে সে। যতবার সম্ভাবনার উপক্রম হয়েছে, ততবারই নিজেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছে যাবতীয় পার্থিব সম্পর্ক থেকে।
হঠাৎ করেই, এক তরুণী সহযোদ্ধার সঙ্গে মিছিলে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে একদিন আবিদের মনে হয়, বাস্তবের কারু সাথে স্বপ্নের মানুষীর মিল খুঁজে পেলেই যেন সে বর্তে যায়। ওরা দুজন মিলে হাঁটিয়াছে বহুদিন পতেঙ্গার সৈকতে, রাঙামাটির সেতু জুড়ে, সীতাকুণ্ডের পাহাড় আর চিম্বুকের মেঘের ভেতর। এইভাবে একদিন দুজনের দুটি আলাদা জীবনযাপন হয়ে গেল যৌথ জীবন। এরই মাঝে গ্লাসনস্ত- পেরস্ত্রেইকার পরের ঘটনা প্রবাহে ওর স্বপ্নভঙ্গ হয়ে যায়। আঘাতটা সয়ে নিতে পেরেছিল তরুণী সহযোদ্ধার (ততদিনে ‘সহচরী’) সান্নিধ্যে, সান্ত্বনায়। প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশুনা শেষ হয়ে যায়, জোরদার হয়ে ওঠে জীবনের দাবি। সব পথের শেষে লেখা দেখতে পায় ‘নো ভ্যাকেন্সি’- চাকরি কোথাও নেই। ‘আয় তবে সহচরী …’ এ প্রস্তাবটুকু আর গলা খেলিয়ে বলার শক্তি- সাহস থাকে না। চাকরি খুঁজতে খুঁজতে জুতোর হাফসোল ক্ষয়; গতানুগতিক গল্পের মতো সহচরীর বিয়ে হয়ে যায় একদিন। আবিদ জাফরের একটা চাকরি অবশেষে হয়- ‘তুমি তখন অন্য কারো, অন্য কোনও ঘরে’।
আবিদ, রাশিদ, কিংবা সাফায়েত – সবারই এমন ক্রান্তিলগ্ন আসে আবিদ জাফরের ভাবতে বসার সময়টা সময়ের বেশ আগে এসে গেল। সে যদি জীবনের স্বাভাবিক তিন পর্বান্তর শেষে মিছা দুনিয়ার ইতিহাসটা নিয়ে ভাবতে বসতে পারতো –
“ শিশু না কাল গেল হাসিতে খেলিতে
যৌবনকাল গেল রঙে
বৃদ্ধকাল যাবে ভাবিতে ভাবিতে …”
তার মানে কি এই দাঁড়াল যে, আবিদ জাফর ও তার বন্ধুরা যেহেতু তিনটি চ্যাপ্টার ক্লোজড করে এনেছে, আজ তাই সে দাঁড়িয়ে আছে বার্ধক্যের কালো বারান্দায়? এমন কোনো কথা নেই যে এই আটতিরিশ- ঊনচল্লিশে সে নতুন একটা উপন্যাসের নায়ক হতেই পারে না! কিন্তু আমরা তো দেখলাম স্রেফ বিশ্বাসযোগ্যতা হারানোর আশংকায় সে তথাকথিত নিয়তির চক্রে ঢুকে পড়তে যাচ্ছে।
এখনো অবশ্য সে ভাবছে।
সাফায়েত এখানে ফোড়ন কাটছে
ছোটগল্পে খুব বেশি বর্ণনার সময়- সুযোগ নেই। ঘটনার ঘনঘটা দেখানোর নিয়ম নেই। সেসব নিয়ম থাকলে আবিদের বিয়ে-থা দিয়ে গল্পটা শেষ করতে পারতাম। তাতে আমার শান্তি হতো। তাহলে হয়তোবা পাঠকের অন্তরে অতৃপ্তি থাকে না। এখানে আবারও সেই চক্র। তাহলে কী আর করা! পাঠক, চলুন, আবিদ জাফর তার দ্বিতীয় রোমান্টিসিজমের ভাবনা জ্বরে পুড়তে থাকুক। হতভাগাটাকে অইখানে রেখে আমরা বরং আধুনিক কোনো গল্প পড়তে বসি ‘চমৎকার! ধরা যাক দু-একটা ইঁদুর এবার’!
এটা রাশিদেরই ঘটনা
বলছিলাম, সংসারী হয়ে রাশিদের এখন নতুন জীবনধারা- ‘আবার না ভোর হতে/ বাজারের থলি হাতে/ মধ্যবিত্ত জীবনযাপন’। ধীরে ধীরে কীভাবে তার লেখালিখি কমে গেল, সে সম্পর্কে শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে আমার কাছে ইনিয়ে বিনিয়ে এখনও নানারকম জবাব দিয়ে থাকে। সে সব চিঠিতে আবার নতুন ভাবে লেখা শুরু করার অস্পষ্ট একটা ইচ্ছে জানান দিয়ে, পুরনো দু’চার লাইন লেখাকে আট-দশ লাইনের একটা পদ্য বানিয়ে পাঠায়। আমার কাছে এক বছর আগে লেখা চিঠির অংশবিশেষ তুলে দিচ্ছি-
“কয়েক দিন আগে টাইফয়েড থেকে উঠলাম। রোগের কারণেই কিনা জানি না, বিষাদে ভুগছিলাম। পুরনো লেখার একটা লাইন খুঁজে পেলাম, ‘জ্বর খুলে দিল কবিতার চোখ’- লাইনটা ‘কাফকার জামা’ নামের কাব্যগ্রন্থের ভেতরে শিল্পী খালিদ আহসানের একটা রঙিন ইলাস্ট্রেশনের ওপর লিখে রেখেছিলাম- ’৯৪-’৯৫ তে হবে। এর সঙ্গে আরো দু’তিন লাইন লিখলাম:
“কতোবার
জ্বর এসে দিয়ে যায় কবিতার চোখ
জ্বরের প্রেরণা নেমে যায়
হেলাফেলায়
এন্টিবায়োটিকে।
আমৃত্যু জ্বর চাই, স্থবিরতা চাই।
‘স্থবিরতা কবে তুমি আসিবে বলো তো’? ”
এই কবিতা লিখে উঠতে পারার পরেও রাশিদ আনোয়ার স্বস্তি বা তৃপ্তি পায় না। সম্ভবত দশ বছর আগে লিখলে এই কবিতাটি আরো শিল্পমানসম্মত হতো এরকম ধারণা হয় তার। আমি আমার বন্ধুর মন বুঝতে পারি, ওর দুই লাইনের মাঝখানের অনুক্ত কথাও আমি পড়ে ফেলতে পারি। বর্ণাঢ্য ক্যাম্পাস জীবনে সে ছিল আমার প্রিয় কবি, আমি ছিলাম তাঁর প্রিয় সম্পাদক, ডাকতো ‘গুরু’! শুনুন, এর পরে কী ভীষণ কথাগুলো অবলীলায় লিখেছিল সে:
রাশিদের মর্মস্পর্শী চিঠি বিষণ্নতায় ঘুমুতে পারছিলাম না। ঘুরে ফিরে একটি কথাই মনে হচ্ছিল আমি একজন প্রতিবন্ধী … আমি প্রতিবন্ধী হয়ে যাচ্ছি। মেটামরফোসিসের গ্রেগর সামসার কথা মনে পড়ছিল। ভাবছিলাম, আমি জগতের সবচেয়ে সুখী লোক— এই কথাটি উপজীব্য করে অনেক বড় একটা লেখা লিখে ফেলা যায়; কোনো মিথ্যাচার হবে না। তারপরেই ভাবছিলাম আমি জগতের সবচেয়ে দুঃখী মানুষ- এই কথাটিকে স্ফটিক করে অনেক বড় একটা হীরে মানিকের খনি পাওয়া সম্ভব- এই লেখাতেও কোনো মিথ্যা কথা লিখতে হবে না। … কিন্তু তা কী করে যুক্তিপূর্ণ হয়! দুটো কথাই তো আর একসঙ্গে সত্যি হতে পারে না। একটাকে সত্যি হতে হবে। এ যে ভীষণ সঙ্কট! আমার কাছে দুটো চিন্তাই সঠিক মনে হচ্ছে। এ কী তবে মনোবিকলন? মনের কোনো জটিল অসুখের সূত্রপাত হচ্ছে আমার? তখন আবারও চিন্তার শুরুটা মাথায় এল, আমি প্রতিবন্ধী হয়ে যাচ্ছি। এ যে বিরাট সঙ্কট! মাথায় হঠাৎ আলোর ঝলকানি খেলে গেল। লিখতে হবে। অন্তত লিখতে শুরু করার চেষ্টা করতে হবে। লেখালিখি করাটা ছিল আমার জীবনযাপনের অংশ। দীর্ঘদিন ধরে সে অঙ্গের হানি হয়েছে। তাই সম্ভবত অবচেতন মন জ্বরের সুযোগে আমার সচেতন মনে বার্তাটুকু পৌঁছে দিচ্ছে যে, তুমি প্রতিবন্ধী ছাড়া আর কী! আমার বিশ্বাস জন্মাল, লিখতে শুরু করলেই এইসব ভাবনা থেকে মুক্ত থাকতে পারব। এই সিদ্ধান্তে আসার পরই আমি বিপদমুক্ত হলাম এবং পরের রাতটুকু ঘুমাতে পারলাম।
সাফায়েতের ডায়েরি
চিঠি পড়তে পড়তে দেখতে পাচ্ছিলাম অপ্রকাশের ভার নিয়ে কেমন ছটফট করছে রাশিদুল আনোয়ার। পরের অংশটুকু পড়ে করুণা নয়, বড় মায়া হলো একসময়ের উজ্জ্বল তরুণ কবির জন্য। এরপরে সে আকস্মিকভাবে লিখেছে-‘জার্নাল লেখা যায়। নির্মলেন্দু গুণ ঢাকার বর্ণাঢ্য কবিজীবনে যাত্রাবিরতি দিয়ে এসে যেরকম ময়মনসিংহে বসে বসে ঢাকার কবিজীবনে প্রবেশ না করতে পারার বেদনাগুলো ‘নির্গুণের জার্নালে’ লিখে রাখতেন- সেরকম। দু বছর আগে একবার জার্নাল লিখতে শুরু করেছিলাম। একাধিকবার ডায়েরি রাখতে আরম্ভ করে ব্যর্থ, জার্নাল লেখার চেষ্টাও ব্যর্থতার মুখ দেখেছিল। তখন জার্নাল লেখার খাতাটিতে বরং বেশি তৎপরতা দেখতে পাচ্ছি গত পাঁচ বছরে টুকটাক কোথায় কী লিখেছি, সেগুলোকে সুন্দর করে জড়ো করায়। সবই অসম্পন্ন লেখা। দুর্বল সাতকাহন। যেনবা ‘ছিন্নপত্রের’ পান্ডুলিপি হচ্ছে কিংবা যেনবা ওই কাজটি করতে পারলেই আবার কবিজীবন শুরু করা যাবে। কতটা সার্বক্ষণিকতা দাবি করে কবিতা সেটা তো আমার জীবনের মূল্যবান বছরগুলোর বিনিময়ে বুঝতে পেরেছি।’
পাঠক, তাহলে কী লিখবে আমার বন্ধু রাশিদুল? না লিখলে তো সে অসুস্থ হয়ে পড়বে; আমার সন্দেহ এতে সে মারাও যেতে পারে। নিজেকে মানসিকভাবে সুস্থ রাখার জন্য তাকে লিখতে হবে- এ কথা আমিই তাকে বারবার মনে করিয়ে দিই। নাকি আমার তাগাদাগুলো বিশাল এক প্রত্যাশার চাপ হয়ে বাংলাদেশের ব্যাটিং অর্ডারের মতো ভেঙ্গে যাচ্ছে রা-শি-দু-ল-আ-নো- য়া-র! আমি কোনো দিক নির্দেশনা দিতে পারলাম না। তাকে চিঠি লেখা বন্ধ করে একরকম পালিয়েই গেলাম তাঁর জীবন থেকে। আমার নতুন ঠিকানাটা তাকে আর দেওয়া হয়নি। বন্ধু-পরম্পরা খুঁজে সে আমার ঠিকানা বের করে ফেলবে অতটা উদ্যমী হতে পারবে না ছা-পোষা বন্ধুটা। মাঝে-মধ্যে অপরাধবোধে ভুগব, সেই সময়টুকুনও তো এই ব্যস্ত নাগরিক জীবনে নেই।
সাফায়েতের ফুটনোট
বছর ঘুরতে খবর পাওয়া গেল, রাশিদুল আর নেই। ‘মরিবার হল তাঁর সাধ!’ হ্যাঁ, অস্বাভাবিক মৃত্যু। বন্ধুর অস্বাভাবিক মৃত্যু বিষয়ে আপনাদেরকে বেশি তথ্য জানাতে চাচ্ছি না; এ জন্যে আমি দুঃখ প্রকাশ করছি। আপনাদের জানবার প্রয়োজনটাই বা কী?
সাফায়েত যেভাবে বন্ধুদের গল্পগুলো লিখতে থাকে কিন্তু শেষ করতে পারে না
আজ সে আবার একটি গল্প লিখতে বসেছে সকালের আলস্য পর্ব, নাশতা পর্ব ইত্যাদি শেষ করার পর। লিখতে বসে আত্মজীবনীর হাজারটা টুকরো চোখের সামনে দুলে উঠছে, গল্প নয়, কোলাজ। বন্ধুদের মুখগুলো ভেসে উঠছে; শুধু মুখ, কোনো গল্পের সূত্র নয়। আরেক রাউন্ড চা খেতে খেতে গল্প লেখার বিবিধ বিড়ম্বনা ও সংকটগুলো ভেবে দেখছিল সে- ‘ঝামেলার যতগুলো দিক আছে’। গল্প যেনবা সুকুমার বড়ুয়ার ‘অসময়ে মেহমান’ যিনি সব কথাতেই ‘ঠিক আছে ঠিক আছে’ বলছেন; কিন্তু তাকে যথাযথ আপ্যায়ন করার মত প্রস্তুতি নাই। অকস্মাৎ গল্পকারের চোখের সামনের দেয়ালজোড়া বিশাল এক কাহিনীর ক্যানভাস ফুটে ওঠে। ক্যানভাসটি ধীরে ধীরে ক্যাম্পাসের সবুজ মাঠ হয়ে যায়। শীতের সকাল। একজন দুজন করে তার বন্ধুরা মাঠের এক কোণে রঙিন তাঁবুতে এসে রেজিস্ট্রেশন করছে। কেউ একা, কেউবা দারাপুত্রকন্যাসহ। সবাই ফুরফুরে মেজাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পরস্পরের সঙ্গে করমর্দন, আলিঙ্গনের মাধ্যমে কুশল বিনিময় করছে। কথায় কথায় বর্তমান থেকে দ্রুত অতীতে ফিরে যেতেই সবাই আরাম বোধ করছে। এরই ফাঁকে সুভেনিরে ছাপা হওয়া ছবি আর মজার কমেন্টগুলো নিয়ে টুকটাক আলোচনা, চা-চক্রে বসে যারা আসেনি তাদের না আসার কারণসমূহ জল্পনা-কল্পনা, দূরের মঞ্চে বাদক দলের সঙ্গে জনপ্রিয় গায়ক-গায়িকাদের সুরের মূর্ছনা শুরু হয়ে যাওয়া, দুপুরে মেজবান শেষে সবাই মিলে সমুদ্র বিহারে যাওয়ার চাপা উত্তেজনা – এই বর্ণিল ঘটনাগুলো অনুষ্ঠিত হয়ে চলে গল্পকারের ঘরের অফ হোয়াইট দেয়ালের কল্পিত ক্যানভাসে ততোধিক কল্পিত সবুজ ঘাসের মাঠে। সেই মাঠে রাশিদও ঘুরছে, ফিরছে। কিন্তু সাফায়েত বা আবিদ তাঁকে দেখতে পায় না। সাফায়েত হয়তো আনন্দের দিনে বিষাদ বা শোকের স্মৃতি মনে করতে চায় না। আর আবিদ জাফর হয়তো রাশিদের বদলে এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকে। কিংবা রাশিদকে লুকিয়ে রেখে এসেছে উন্নয়ন আমলের কোনো ফ্লপি ডিস্কে, হরপ্পা লিপির পাঠ উদ্ধার করা গেলেও এইসব ফ্লপির জাভালিপি রহস্যগুলো র্যাঁবোর জাভাদ্বীপের রহস্যের মতোই একশো বছর পর উদ্ধার হবার অপেক্ষায় থাকবে। আবার, রাশিদুল আনোয়ার মরে না গেলে আবিদ জাফর তো বেঁচে থাকতে পারবে না।
গল্পকার, মানে সাফায়েত হঠাৎ করে সংবিৎ ফিরে পায়, হিব্রু ভাষায় একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে মাঝ রাত্তিরের দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে ওঠে: ‘এলি, এলি, লামা সাবাক্তানি!’ ু ও আমার ঈশ্বর, ও আমার ঈশ্বর, তুমি কেন আমাকে পরিত্যাগ করলে!
এই গল্প ভাবনাটি হয়তোবা সামনের কোনো ছুটির দিনের অবকাশে লেখা হয়ে যেতে পারে।
মোশতাক আহমদ
কবি, কথাসাহিত্যিক, অনুবাদক, জন-স্বাস্থ্যবিদ